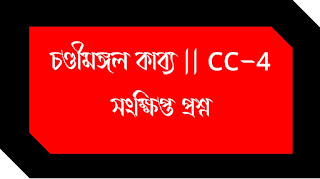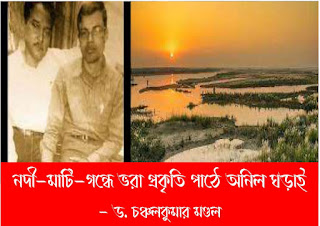জাতীয় সংহতি ও 'মন্দিরে আজান' ভবেশ বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাস
জাতীয় সংহতি ও ‘মন্দিরে আজান’ ভবেশ বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাস
— ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত
মহাবিদ্যালয়
“মানুষ
একদিকে মৃত্যুর অধিকারে, আর একদিকে অমৃতে; একদিকে ব্যক্তিগত সীমার, আর একদিকে
বিশ্বগত-সীমার বিরাটে। এই দুয়ের কোনোটাকেই অস্বীকার করা চলে না।” — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
 |
| মন্দিরে আজান - ভবেশ বসু |
“শুধু
জানি,
বিশ্বপ্রিয়ার
প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে
হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান।”
তাই যে ধর্মের মধ্যে আছে চির শান্তির মন্ত্র, আছে সত্যান্বেষণের পথ, সেই ধর্মের কথাই বলেছেন শ্রীচৈতন্যদেব-বুদ্ধ-নানক-যীশুখ্রীষ্ট-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সহ লালন ফকির-কাজি নজরুল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল কবি-শিল্পী মহান মনিষীগণ। ইসলামের ‘আল-হক-কুন’ অর্থে ঈশ্বরই সত্য। সেই ‘সত্য’কে উপলব্ধিই হল মা
নুষের ধর্ম। মানবধর্ম, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ধর্মের বিরোধ, যে দ্বন্দ্ব, যে মত পার্থক্য তার সবই একেবারে বাহ্যিক। অথচ, আরব দুলাল হজরত মহম্মদ আর ব্রজেররাখাল শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই সহজ ‘সত্য’কে উপলব্ধি করতে হলে ভবেশ বসুর সাম্প্রতিক ‘মন্দিরে আজান’ উপন্যাসটি অবশ্যই পাঠ প্রয়োজন। যে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এই সময়কার কথাশিল্পী হিসাবে ভবেশ বসু সকল ধর্মের ঊর্ধ্বে শাশ্বত প্রেমধর্মকে, পবিত্র বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে মানবধর্ম রূপে প্রতিষ্ঠিত করার পথ বাৎলে দিয়েছেন।
 |
| মন্দিরে আজান - ভবেশ বসু |
অবশ্য শ্রীমানবসুর পূর্বে অনেকেই এই
হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্বের মতো বিষয়কে শিল্পরূপ দিয়েছেন। যেমন, মানিক
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কোলকাতার দাঙ্গা’, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ‘হিন্দু-মুসলমান’ সহ
উপন্যাস ‘চতুরঙ্গ’তে ও হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব গত বিষয় চিত্রিত হয়েছে। আবার,
হিন্দু-মুসলমানের উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে ওপার বাংলার গল্পকার ওয়ালী উল্লাহ লেখেন— ‘একটি তুলসী গাছের কাহিনী’,
এছাড়া তাঁর ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধ বলিষ্ঠ উচ্চারণ ‘লালসালু’ উপন্যাস। আখতারুজ্জামান
ইলিয়াস-এর গল্প ‘খোঁয়ারি’তে সমরজিৎ চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেশভাগ, দাঙ্গা— এ সবই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে শিল্পের শাসনে। আবার এপার বাংলার গল্প ‘আদাব’ তো
হিন্দু-মুসলমানের আত্মীয় হয়ে ওঠার গল্প হিসাবে চিত্রিত করেছেন সমরেশ বসু। বিনুর চোখ
দিয়ে দেশভাগ, দাঙ্গা সবই ধরা পড়েছে প্রফুল্ল রায়ের ‘কেয়াপাতার নৌকা’ উপন্যাসে।
এমনকি ‘ভাগাভাগি’ উপন্যাসেও সেই চিত্র ধরা পড়ে। দেশভাগ, হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্ক
নিয়ে লেখা অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’। যেখানে সোনা আর
ঈশমের আন্তরিক অনুভূতির কোন মূল্য থাকে না। এইরূপে নবারুণ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু
করে সাম্প্রতিক কালে প্রতিভা বসুর ‘সমুদ্র হৃদয়’ এবং নীললোহিতের ‘পূর্ব-পশ্চিম’
উপন্যাসে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ দুই বঙ্গেরই সাধারণ মানুষ কেমন করে
ধীরে ধীরে অনিশ্চিত অন্ধকারে এগিয়ে গেছে, তাই দেখিয়েছেন এই উপন্যাসে। এই ধারাস্রোতে
ভবেশ বসুর ‘মন্দিরে আজান’ উপন্যাসটি তার ব্যতিক্রম নয়। পূর্ব-বাংলার প্রাবন্ধিক
আবুলফজল তাঁর ‘মানবতন্ত্র’ প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্থায়ী
সম্ভাবনার স্বপক্ষে ‘একথা আমার কাছে সোনার পাথর বাটি’ বলে মনে করলেও বহু রক্তক্ষয়ি
দ্বন্দ্ব আর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর, ঐ হিন্দু-মুসলিম দুই ধর্মের নর-নারীকে এক
ঐক্যসূত্রে বেঁধে ফেলার নয়া সম্ভাবনার দিক বাৎলে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক ভবেশ বসু তাঁর
এই উপন্যাসে।
উপন্যাসটি
প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ, ১৪০১-এ। এরপর দীর্ঘ বাইশ বছর পর ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৪২৩-এ
পুনরায় এই উপন্যাসের বর্তমানে আরো বেশি প্রাসঙ্গিকতার দাবী মেনে নিয়ে দ্বিতীয়
সংস্করণ করেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেন,—
“বিভাজন
শুধু জলে-স্থলে নয়, মানুষের রক্তে এবং শরীরে। এখন এই রোগে আক্রান্ত দেশ ও পৃথিবী।
এমনটি হওয়ার কথা নয়। মানুষ মানুষের জন্য, এই আহ্বান ছিল। এখনও সুদৃঢ় কণ্ঠে সেই একই
ঘোষণা। আজ আমার নয়, সকলের।— ”
ঔপন্যাসিক মূলত: কবি। তাঁর প্রকাশিত দুটি গল্প
গ্রন্থ ছাড়া, কাব্যগ্রন্থ ‘প্রতিবেশী চাঁদ’ (১৯৮৪) থেকে অধুনা ‘লাশ সাঁতার’ (২০১৮
যুগ্ম), ও ‘একটি গবেষণাপত্র’ (২০১৮) পর্যন্ত কুড়িটি গ্রন্থের স্রষ্টা। একজন কবি
হিসেবে প্রচণ্ড রকম শিল্পের এবং সমাজের দায়বদ্ধতায় তাঁর কাব্যিক চেতনা ময় উপলব্ধি
পথে উপন্যাসের পাতার পর পাতা জুড়ে রয়েছে অসংখ্য বিবেক সমৃদ্ধ আলোকোজ্জ্বল
বক্তব্যগুলি। উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণে কল্যাণ চরিত্রের মধ্য দিয়েও স্বয়ং
ঔপন্যাসিক ভবেশ বসু মানুষের মধ্যে এত ভাঙন, এত বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, পরাজয়; আর
লক্ষ্য ভ্রষ্ট মানুষের হিংসার উন্মাদনা দেখে ব্যথিত চিত্তে বলেন;—
“মানুষ
প্রতিশ্রুতি ছিল, কোটি কোটি হস্তের বন্ধনে তারা হৃদয় সমুদ্র মন্থন করবে। আর সেই
মন্থনের অমৃত মানুষেরই পায়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে চাইবে অমরত্ব।”
প্রকৃতি
প্রেমিক লেখকের তুলির টানে উপন্যাসের শুরুতেই ফুটে উঠেছে সেই নিসর্গ প্রকৃতির
রূপচ্ছটার বিচিত্র লীলা চিত্র। যে চিত্র, ধ্বনি এবং সংগীতে মুখরিত হয়ে-বিশ্বের আনন্দ
যজ্ঞের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে। ধর্মের দাঙ্গায় ক্ষতময় রাষ্ট্রের দেশভাগের যে
যন্ত্রণা, নীড়হারা মানুষের যে ভিটে-মাটির শেকড় ছেঁড়ার দগ্ধ-ক্ষত, সেই দুঃখ ব্যথাকে
চির নির্বাসন দিতে চেয়ে কথাশিল্পী প্রকৃতির বুকে ঐ নীড়ে ফেরা পক্ষীকুলের অনুষঙ্গ
এনে তাই বলেন— ‘আমার ঘর হারিয়ে ও তাই আনন্দ।’ বৃক্ষ যেমন
শত ঝড়-জল এড়িয়েও দাঁড়িয়ে থেকে ফুল-ফল দিয়ে যায়, পথিককে দান করে ছায়া;— তেমনি, মানুষ ঐ বৃক্ষের মত শত দাঙ্গা আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরও শত
দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার গ্লানি ভুলে নিজেকে রাঙিয়ে তোলে ঐ বৃক্ষের সবুজ পাতা মেলে
ধরার মতো। তাই ঝড়-জল, দুঃখ-যন্ত্রণা মুছে ফেলে কথাশিল্পী ভবেশ বসু নদীর কাছে
প্রশ্ন করেন,— ‘বল নদী, কোথা থেকে এসেছো?’ — আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ‘ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে’ বেরিয়ে নদীকে এমনি প্রশ্ন
করে ছিলেন। সেখানে জগদীশচন্দ্র বসু আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার আলোকে পুরাণ অনুষঙ্গ
টেনে (উত্তর: ‘মহাদেবের জটা হইতে’) আনলেও, এখানে ভবেশ বসু কোনো বিজ্ঞান কিম্বা,
পুরাণের আশ্রয় না নিয়ে, মানব মনের হৃদয় মন্থনে নদী পথের উৎস সন্ধানে জেনেছিলেন
— ‘আনন্দ থেকে’ই তার আগমন আবার ‘আনন্দে’ই তার ফিরে যাওয়া। অর্থাৎ, বিশ্বের
এই আনন্দ যজ্ঞে মহামানবের মহামিছিলের অমোঘ বাণীর স্বরও সুরের অনুসন্ধান করে
ফিরেছেন কথাশিল্পী তাঁর এই উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রথম পর্বেই অনুভবে খুঁজে পেতে
চেয়েছেন অক্ষর শিল্পী ‘আমিত্ব’কে। এই ‘আমিত্ব’কে উপলব্ধির চেষ্টা মানে ‘আত্মা’কে
জানা। ‘আত্মা’কে জানা মানে, ‘সত্য’কে জানা। এই ‘সত্য’কে উপলব্ধিই হল
শাশ্বত-মানবধর্মকে উপলব্ধি। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন—
‘তাহলে আমি কে?’ উপলব্ধির চেতনা পথে সত্যিকারের মানব সন্তান কিনা, সেই উত্তরের
আশায় প্রশ্ন রাখেন সমাজের কাছে— ‘আমি কি মানব সন্তান?’ কারণ,
তিনি মনে করেন ‘পৃথিবীর সকল মানুষ আজও ‘মানুষ’ নয়।’ তাই-তো বিশ্বকবি এই মানুষ হয়ে
ওঠার সাধনায় জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে বাঙালীদের তৈরী থাকতে বলেন,—
 |
| আধুনিক কথাসাহিত্যিক ভবেশ বসু |
“পুণ্যে
পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ
হইতে দাও তোমার সন্তানে।
সাতকোটি
সন্তানের হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো
বাঙালী করে, মানুষ করোনি।”
[‘চৈতালি’; ‘বঙ্গমাতা’]
সত্যিকারের ‘মানুষ’ হয়ে ওঠার সামাজিক দায়বোধ
স্বীকার করে, প্রখর সমাজ সচেতক কথাকার ভবেশ বসু তাঁর এই উপন্যাসে বিশেষ কোন গল্প
তথা কাহিনী কিম্বা, চরিত্রের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে সেই চিরন্তন রাষ্ট্রনৈতিক
চিন্তা-চেতনার ওপর জোর দিয়েছেন। আর উপন্যাসের শুরুতে তাই ‘আমিত্ব’কে জানবার সাধনায়
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রসঙ্গ ঔপন্যাসিক তাঁর কাব্যিক চেতনা পথে ফুটিয়ে
তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথও মানবতার সেই প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন সূত্রে বলেছেন,—
“মানুষের
প্রকাশই শ্রেষ্ঠ যা একান্ত ব্যক্তিগত মনের নয়,
যাকে
সকল কালের সকল মানুষের মন স্বীকার করতে পারে।
এই
সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করে উপলব্ধি
করাতেই
মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন
উন্নতির
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে
উঠেছে,
তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা।
ইতিহাসে দেখা যায় মানুষের আত্মোপলব্ধি
বাহির থেকে অন্তরের দিকে আপনিই গিয়েছে,
সে অন্তরের দিকে তার বিশ্বজনীনতা, সেখানে
বস্তুর বেড় পেরিয়ে সে পৌঁছেছে বিশ্বমানস
লোকে— যে লোকে তার বাণী, তার শ্রী,
তার মুক্তি।”
[‘মানুষের
ধর্ম’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]
এই দুর্লভ
মনুষ্যত্ব সাধনার শিল্প ফসল ভবেশ বসুর ‘মন্দিরে আজান’ উপন্যাস। যে উপন্যাসের আলোক
পথের যাত্রী রোশনা ও তপনের চিন্তা ও চেতনালোকের মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে জীবন সাধনার
মূলকথা। শুধু এই নয়, উপন্যাসের কালো-কালো অক্ষরে আগুন রঙা কথাকলায় ঝল্সে উঠেছে— লেখকের ধর্মচিন্তা, সমাজ চিন্তা,
বিশৈক্যানুভূতি, প্রকৃতি ও বিশ্বমানব চিন্তা এমনকি, প্রেমসাধনাও জীবন চেতনার
চিরন্তন প্রকাশ। লেখকের মুক্তচিন্তা, শুভবুদ্ধি ও স্বচ্ছ যুক্তিতে উপন্যাসের
কাহিনী কিম্বা, চরিত্র অপেক্ষা আলোকোজ্জ্বল বাণীমুগ্ধ স্থিতধী বক্তব্যই মুখ্য হয়ে
উঠেছে।
জাতীয়
সংহতির সহজ সমীকরণের পথ বাৎলে দিতে জোড়ায়-জোড়ায় উঠে এসেছে এক গুচ্ছ চরিত্র। যেমন,
রহমান সাহেবের কন্যা রোশনা, যে নারী কোরান, বাইবেল সহ বেদ, গীতায় সুপণ্ডিত। রোশনার
পাশাপাশি উঠে এসেছে লোকনাথ চক্রবর্তী পুত্র তপন। যে তপন সমাজে ন্যায় ও সাম্য
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছে। যে তপনের আর এক নাম-‘সূর্য’। তাই তপন চরিত্রের মধ্য
দিয়ে উপন্যাসের পাতায়-পাতায় মানবতার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। এই দুই আলোকোজ্জ্বল চরিত্রের
ঠিক বিপরীতে উঠে এসেছে ‘রজনীক্লাবে’র ছবি। যা সামাজিক অবক্ষয় আর ব্যাধির প্রতীক।
যে ক্লাবকে ঘিরে উগ্র আধুনিকতার তীব্র ভোগবাদের নগ্ন ছবির অনুষঙ্গ রূপে নাচ, গান,
জাঁক-জমক আড়ম্বর সর্বস্ব লক্ষ্য করা যায়। ডা: নন্দী যে ক্লাবের সভ্য। তারও এক সময়
জাগরণ ঘটেছে। বিশ্বাস আর মূল্যবোধ যার ইতিহাসে নেই সেই নারী হল উলি রায়। মিসেস উলি
রায় উগ্র আধুনিক নারী সমাজের প্রতীক। আবার, ফণী দত্তের ছেলে দেবাশিষের ভোগবাদী
প্রেমের কাছে কালী মুদ্দিনের মেয়ে নুরজা হার মেনেছে। অথচ, ঐ নুরজাকে চায় রহুল আমিন
মল্লিক। গুরুচরণ সিং-এর পুত্র কল্যাণকে রহুলের রক্ত দেওয়ার মধ্য দিয়ে জাতি গত
সাম্য প্রতিষ্ঠার ছবি লক্ষ্য করা গেছে। আবার, তপনের বন্ধু সুজয়কে ভালোবাসে লিলি।
অথচ, ঐ সুশীলবাবুর কন্যা লিলির পূর্ব প্রেমিক ছিল কল্যাণ। আবার, নাইলাকে ভালোবাসার
অপরাধে খুন হয় দিব্যেন্দু। অথচ, ইসলামের মর্যাদা স্বীকার করেও অখণ্ড জাতি
প্রতিষ্ঠার সংকল্পে অনড় সাদেক আলি। আদর্শবাদী শিক্ষিত যুবক সজল। অথচ, বিকৃত রুচির
ফসল-সজল ভালোবাসে রাকাকে। উপন্যাসের জাফেদ বিয়ে করে হিন্দু রমণী মাধুরীকে। ডা:
নন্দী কামনা করে কণিকাকে। এছাড়া, নীলাদ্রি, রুকিয়া, সুভাষ, কাঞ্চন প্রভৃতি
চরিত্রগুলি একে একে উপন্যাসে ভিড় জমিয়ে জাতীয় সংহতির পথ বাৎলে দিতে সাহায্য করেছে। উপন্যাসের
আরও এক নারী মাধুরী। যে নারী কপালে পূজার সিঁদুর আর লালপাড় শাড়ি পরে চলেছে নামাজে।
যে মাধুরীকে দেখে কণিকা হতবাক্। সমস্ত উপন্যাস পাঠককেও হতবাক্ করিয়ে দিয়ে যে মাধুরী
বলতে পেরেছে,—
“আমি
ভালবাসি গোটা পৃথিবীর ধর্ম।
পোশাক,
আচার-অনুষ্ঠান এ সকল নিজস্ব রুচি।”
প্রেম শাশ্বত চিরন্তন। যে প্রেমের হাত ধরে
বিশ্বকে জয় করার সহজ পথ দেখিয়ে গেছেন শ্রী চৈতন্য, নানক, বুদ্ধদেব সহ সকল মহান
মনিষীগণ। ঔপন্যাসিক ভবেশ বসু তাঁর উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে সেই প্রেমের সুদৃঢ়
বন্ধনে বেঁধে দিয়ে বিশ্বপ্রেমের বাণী ঘোষণায় ভালোবাসার মহিমা সম্পর্কে বলেছেন;—
“পৃথিবীর
নিরাপত্তা হল ভালবাসা। আর এই ভালবাসার রঙকে নানান তুলির টান দিতেই মানুষের আসা ও
কাজ করা। তাই মানুষ শিল্পী।”
এমন চিরাচরিত, প্রথাগত জীবন প্রবাহের সত্যতাকে
আর কে বা তুলে ধরতে পারে এমন করে? জীবনকে নিবিড় ভাবে ভালোবাসতে না জানলে;
ভালোবাসার মহিমাকে এমন করে উপলব্ধি র পথে তুলে ধরা যায় না। যা ভবেশ বসুর কবি মনের
চিন্তা-চেতনার মর্মবাণীতে ধরা পড়েছে। আসলে, মধ্য যুগীয় কবির সেই প্রেমানুভূতি,—
“অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিম্ব
ফুলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।।”
ঔপন্যাসিক
ভবেশ বসু সেই রসজ্ঞ কোকিল রূপে মানব জীবনের চিরন্তন প্রার্থনীয়, একান্ত কাম্য
বস্তু প্রেমের অমর মহিমাকে বিচিত্র রূপে-রঙে-রেখায় শিল্পীর তুলি দিয়ে উপন্যাসের
চরিত্র সকলের মধ্য দিয়ে এঁকেছেন।
উপন্যাসের কথাকলার আঙ্গিকে ছোট ছোট সংলাপের মধ্য
দিয়ে পুনরায় যেন সেই প্রাচীন মহান মুনি-ঋষিদের অমোঘ বাণীর আহ্বান স্মরণের মধ্য
দিয়ে তাঁর স্থিতধী বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ঔপন্যাসিক ভবেশ বসু সেই
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব, মানুষে-মানুষে সন্দেহের দেওয়াল গড়ে ওঠার
এমন বাস্তব-নগ্ন, ভয়ঙ্কর ছবিটা লক্ষ্য করে শিউরে ওঠেন। সেই দেওয়াল ভেঙে ফেলার দুর্বার
আকাঙ্ক্ষায় রোশনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। ঔপন্যাসিক স্বয়ং তাঁর স্থিতধী
বক্তব্যকে রোশনার মধ্য দিয়ে আগুন রঙা কথা কলায় উগ্রে দিয়েছেন। প্রচণ্ডরকম সামাজিক
দায়বোধ সম্পন্ন লেখক হিসাবে তিনি স্বপ্ন দেখেন— যোগীর আশ্রমের মতো সমাজ গড়ে ওঠার। সেই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায়
তিনি রোশনার পিতা রহমান সাহেবের কণ্ঠে ঘোষণা করেন,—
“এমন কেউ
কি আছে, সহস্র বাহু মেলে এই সমাজটিকে যোগীর আশ্রমের মতো গড়ে দেবে?”
কারণ,
সুতীব্র সমাজ সচেতক কথাশিল্পী লক্ষ্য করেন, ধর্মের বলয়ে ঘেরা মিথ্যা শিক্ষার
প্রচণ্ড আস্ফালন। অথচ মানুষ তার সত্যিকারের ধর্ম ভুলে গেছে। ভুলে গেছে যৌবনের
ধর্ম। যে যৌবনের প্রতীক হিসাবে মানুষের সত্যিকারের পথ দেখিয়ে গেছেন স্বামী
বিবেকানন্দ। সেই— ‘যৌবনের ধর্ম লাল। যৌবনের ধর্ম একতা’ তাই
ঔপন্যাসিকের উদাত্ত আহ্বান—
‘সব গুচ্ছ হয়ে ফোটো, একত্রিত হও।’ অথচ, মানুষ তার প্রকৃত ধর্মকে ভুলে
পরস্পরে বিচ্ছেদ ডেকে আনে। মানুষ তার আচরণে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, সে অতীত সভ্যতার
দিকে ফিরে যাচ্ছে। পশ্চিমী উগ্র সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে অহেতুক মানুষ
উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। তাই ঔপন্যাসিক রোশনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের মনের জাগরণ
চেয়েছেন। জেগে ঘুমিয়ে থাকা মানুষ তার আত্ম-জাগরণের মধ্য দিয়ে জীবনের ঐ প্রকৃত
ধর্মের পথ, সত্যের পথ ফিরে পাবে। মানুষ ‘ধর্ম’কে সামনে রেখে (লেখকের
ভাষায়) ‘চৈতন্যের গভীরে তুফান তুলেছে সে সাম্প্রদায়িকতায়’; সেই সাম্প্রদায়িকতার
নামে পরস্পরে হাতাহাতি, রক্তের বন্যা বইয়ে দেওয়া মানে তো সেই আদিম সভ্যতার যুগে
ফিরে যাওয়া। তাই আজ খু-উ-ব প্রয়োজন মানুষকে-মানুষ-ধর্মের মোড়কে নয়; প্রেমের বন্ধনে
বাঁধতে শেখা। যে পথ দেখিয়ে গেছেন মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব। আদ্বিজ চণ্ডালকে তিনি
বুকে জড়িয়ে ধরে আগামী মানব সভ্যতাকে দেখিয়ে গেছেন কিভাবে প্রেমের বন্ধনে বিশ্বকে
বেঁধে ফেলা যায়। তাই তিনি জাত ধর্মের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে প্রবল প্রেমের বন্যায় গোটা
বিশ্বকে এক সূত্রে বেঁধে দিতে পেরে ছিলেন। তাই ঐ মহাপ্রভুর প্রেমের পথ অনুসরণ করে
স্বয়ং ঔপন্যাসিক রোশনার মুখ দিয়ে ঐ তপনকে নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার প্রতি ঘোষণা
করেন,— ‘ভালবাসতে জানলে নিকট দূর সব একাকার হয়ে যায় তপন।’ শুধু এই
নয়; পরবর্তী কালে ঔপন্যাসিক বলেন, ‘গোটা পৃথিবীই আমার দেশ’— এমন
করে ভাববার আত্মবিশ্বাস আজ বড় অভাব বলেই মানুষ এত পরস্পরে বিচ্ছিন্ন। আর তাই
প্রচণ্ড সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন লেখক হিসাবে ভবেশ বসু এক স্বপ্নময় সুদিনের আশায়
মনে করেন,— মানুষ
প্রকৃত সমাজতন্ত্রী তখনই হয়ে উঠবে; যেদিন—
“সকলে
একাসনে থাকবো। স্রোতে গড়িয়ে যাবে এদেশ ওদেশ। যেমন মেঘ জল ঢালে , সূর্য আলো ছড়ায়,
বাতাসে ভেসে যায় বীজ, ফুল গন্ধ বিলায়, জীবন সর্বত্রই প্রসন্ন, দৃষ্টিটা স্পষ্ট— তেমন করে মানুষের অধিকার টুকু
নিয়ে শ্লোগান লেখা এক শিক্ষা। আর এরকম জ্যোতি শত প্রদীপ হয়ে জ্বললে তবেই আমরা
সমাজতন্ত্রী, এখন নয়।”
কিন্তু, আমাদের ঐ প্রকৃত সমাজতন্ত্রী হয়ে ওঠার
পথে বড় অন্তরায় — ধর্মসর্বস্বতা। অন্তঃসার শূন্য ধর্মের ঐ
বাহ্যিক আড়ম্বর হেতু আমরা পরস্পরের মধ্যে বিভেদের দেয়াল গড়ে তুলি। প্রাণের
অস্তিত্বকে করে তুলি বিপন্ন। ধর্মের প্রকৃত অর্থ ভুলে পরস্পরে পৈশাচিকতার পরিচয়
দিই। তাই চিন্তানায়ক ঔপন্যাসিক ভবেশ বসু মনে করেন,—
“...অথচ
মন্দিরে শাঁখ বাজবে। মসজিদে নমাজ। আর গীর্জায় হবে প্রার্থনা সভা। এগুলি
সামাজিক প্রথা, অনুশাসন। ধর্ম নয়।”
প্রকৃত ‘ধর্ম’ অর্থে মানবাত্মার পূর্ণ বিকাশ।
তাই বিবেকানন্দ বলেছেন,—
“মানব অন্তরে নিহিত পরিপূর্ণতার
বিকাশ সাধনই ধর্ম।”
কিন্তু, সেই ‘ধর্ম’কে যখন মোহ এসে আচ্ছন্ন করে
ফেলে, তখন ধর্ম তার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আর সেই গণ্ডীবদ্ধ
সাম্প্রদায়িক ধর্ম বার-বার অন্য ধর্মকে আঘাত করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার
খামখেয়ালিপনায় মেতে ওঠে। আর সেই মোহাচ্ছন্ন ধর্মের পরিণতি হিসাবে বিশ্বকবির বাণীতে
তার ফলাফল বিঘোষিত হয়ে ওঠে;—
“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।”
[‘পরিশেষ’;
‘ধর্মমোহ’]
তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে রয়েছে ঐ ‘ধর্ম’।
যে ধর্ম মানুষ-মানুষে ভেদ রচনা করে, যে ধর্ম মানুষের কোনো কাজে লাগে না, বরং
জীবনের অকল্যাণ বয়ে আনে, সেই ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। কথাশিল্পীর মতে সব সমস্যার
মূলে ঐ ‘ধর্ম’। কারণ, ‘সবাই নিজেদের ধর্মকে বড় দেখে।’ অথচ, মানুষকে ভালোবাসাই সকল
ধর্মের মূল কথা। কথাকার তাই বলেন,—
“সেবা
করাই সকল ধর্মগ্রন্থেরই মুল সুর।
গীতা,
কোরান, বাইবেল কেউ-ই-বহুবাদে
বিশ্বাসী
নয়।”
রহুল চরিত্রের মুখ দিয়ে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের তাই
‘ধর্ম’ সম্পর্কে প্রশ্ন,—
“মানুষকে
ভালোবাসায় যদি ধর্মের অবমাননা হয়,
তাহলে
সে ধর্ম মেনে লাভ?”
এই ‘ধর্ম’ প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রের
বিচার-বিশ্লেষণে রাজা রামমোহন রায়ও এক সময় লিখে ছিলেন ‘ভট্টাচার্যের সহিত বিচার’,
‘তর্কালঙ্কারের সহিত বিচার’, ‘বিদ্যালঙ্কারের সহিত বিচার’ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মের
মন গড়া শাস্ত্র নিয়ে বিতর্কিত সব সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি। হিন্দুশাস্ত্রের
মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করেছেন। বক্তব্য
প্রধান এই উপন্যাসেও ভবেশ বসু কর্ম অনুসারে সমাজের শ্রেণী বিন্যাসে, হিন্দু ধর্মের
শাস্ত্রীয় বিধান প্রসঙ্গে রোশনা চরিত্রের মধ্য দিয়ে এক বিতর্কের ঝড় তুলেছেন। রোশনা
চরিত্রের ঐ যুক্তিনিষ্ঠ তার্কিক বক্তব্যে ব্রাহ্মসমাজের মনগড়া শাস্ত্রের বিধানকে
তছ্নছ্ করে দেয়। যখন ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতীক ঐ লোকনাথ বাবু বলেন:
“সত্ত্বঃ
রজঃ তমঃ এই তিন গুণ ও কর্ম অনুসারে বর্ণসৃষ্টি হল।
সত্ত্ব
প্রধানই ব্রাহ্মণ, অন্যেরা নীচে।”
এমন অকাট্য যুক্তিহীন বক্তব্যের প্রতীবাদে
রোশনার কণ্ঠে স্বয়ং ঔপন্যাসিকের স্থিতধী বক্তব্য;—
“সত্ত্বঃ
গুণ প্রধান হলে যে কোন বংশজাত মানুষই ব্রাহ্মণ হবে; এতো আপনার শাস্ত্রেই লেখা আছে— কাকাবাবু। যে সকল ব্যক্তির ব্যবহার সত্য ও
সুন্দর তারাই শ্রেষ্ঠ। অপর দিকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট মানুষ সকলের ঘৃণার পাত্র হয়। শ্রেষ্ঠ
ব্যক্তি সকল সময়েই জ্ঞানী হবে। ব্যবহারেই তিনি ব্রাহ্মণ।”
এভাবে, একসময় ব্রাহ্মণ যে হিন্দু ধর্মের
শ্রেষ্ঠ জাতি, সেই ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ঔপন্যাসিক
তাঁর যুক্তি নিষ্ঠ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ধর্মের ধ্বজাধারী অহং ব্যক্তিদের বুঝিয়ে
দিয়েছেন। জাতি এক, ঈশ্বর এক, সকল বর্ণ ও ধর্মের মানুষও তাই এক। এই একেশ্বর বাদে
বিশ্বাসী করে তুলতে ঔপন্যাসিক তাই তাঁর পাঠকদের বুঝিয়েদেন ‘ব্রাহ্মণ’ তিনিই,—
“যিনি
ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।
তিনি
নিরাকার। কোন জাতি থেকে ব্রাহ্মণ
শব্দটি
আসেনি। যিনি স্রষ্টার স্বীকার
বা
তার ভজনা করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।...”
আর সেই— ‘আমরা পেলাম বহু আত্মার এক ব্রহ্ম।’ তাই
মানুষে-মানুষে বিভাজন ডেকে আনা মানে ব্রহ্মকে ভাগ করা তথা, পূর্ণ-ব্রহ্মকে না
পাওয়া। ঔপন্যাসিক তাই এই কথাকলার কাহিনী সূত্রে সজল ও রাকার প্রেমের পথের
প্রতিবন্ধক হিসাবে সেই ‘ধর্মে’র অনুষঙ্গ তুলে ধরেছেন। যে ‘ধর্ম’ দুই নর-নারীকে প্রেমের
হাত ধরে মিলতে দেয় না। যার ফল হিসাবে ‘প্রেম হারালো তার চিরাচরিত সুখ ও লাবণ্য।’ একসময়
যে সজল দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল— ‘আমি ভালবাসি রাকাকে। তার
ধর্মকে নয়।’ অথচ, সেই ধর্মের মোহ তাদের প্রেমকে গলাটিপে হত্যায় উদ্যত হয়। প্রবল
হিন্দুত্ববাদী ব্রাহ্মণ সমাজ ঐ হিন্দু-মুসলিম দুই দ্বি-ধর্মের নর-নারীর মিলনকে
পূর্ণতা না দিয়ে বরং তারা ঐ ‘পবিত্র প্রেমের নিগূঢ় বন্ধন ধর্মান্ধতার জালে জড়িয়ে ক্রমশ
হিংস্র হল।’ আর এমন ধর্মের কুয়াশা ঘেরা পরিবেশে— মানুষের মন
থেকে ধর্মের মোহ মুছে ফেলতে তপনের কণ্ঠে স্বয়ং ঔপন্যাসিক ভবেশ বসু ব্যাধিগ্রন্ত
গোটা পৃথিবীর উদ্দেশ্যে বক্তব্য সূত্রে ধরিয়ে দেন জীবনের আসল ‘মাধুর্য’কে; আর দেখিয়েছেন
পবিত্র কল্যাণের প্রকৃত পথ। এমনকি, মানুষের প্রকৃত ‘ধর্ম’
সম্পর্কে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বলেন,—
“...আমাদের
পরিচয় জ্ঞান ও চৈতন্যের আলোয় আলোকিত একটি জীব। আমরা বিশ্বের নাগরিক। মানুষের ধর্ম
সত্য সুন্দর, প্রেম ও পরোপকার। আমরা একই আত্মার আত্মীয়। আমাদের পথ, আমাদের জীবন, ধর্ম-কর্ম-উন্নতি
সকলের জন্য উন্মুক্ত হউক, এই কামনা বাসনাতেই আসবে জীবনের মাধুর্য, পবিত্র কল্যাণ।”
অথচ,
ধর্মের ধ্বজা তুলে মানুষ মানুষকে অবলীলায় পীড়া দেয়। উগ্র স্বাজাত্যবোধ যার বিষ
জর্জর পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি না পেলে বিশ্বাত্মবোধ জেগে ওঠা সম্ভব নয়। সংকীর্ণ
জাতীয়তা বোধের কারণেই তো মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধি করতে
পারে অনায়াসে। রবীন্দ্রনাথ তাই ‘বুদ্ধভক্তি’ কবিতার সূচনাপর্বে মুখবন্ধ হিসাবে
বলেছেন—
“ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে,
আর ভক্তির বাণ মারছে বুদ্ধকে।”
[‘নবজাতক’]
তাইতো দেখা যায় মানুষ, মনুষ্যত্বকে খুঁজে ফিরেও
মনুষ্যত্বহীনতার কাজ করে। এর থেকে মানব জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস আর কি বা হতে পারে?
তাই উপন্যাসের সজল-রাকার প্রেমের অপমৃত্যু প্রসঙ্গে কবি কণ্ঠের আর্তধ্বনি উচ্চারণ
করে বলতে হয়,—
“যৌবনেরই ধর্ম ভুলে প্রেমকে করি জবাই,
অথচ আমরা জীবনে এখন মানবতা চাই সবাই।”
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রনোন্মাদনার দামামা রবীন্দ্রনাথ
শুনেছেন মাত্র; সেই দৃশ্য তাঁর চাক্ষুষ ঘটেনি। কিন্তু, তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর অশুভ
ফলাফল অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন। তেমনি, এই সময়কার কথাশিল্পী হিসাবে
ভবেশ বসুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পথে ধরা পড়েছে রাম মন্দির আর বাবরি মসজিদ নিয়ে
সংঘর্ষের উন্মাদনা। ‘ধর্ম’ই সমগ্র মানব জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক। কালাপাহাড়ের কথা
তাই মানুষ আজও ভুলতে পারেনি। ধর্মের ক্ষতিকারক প্রভাব লক্ষ্য করে একসময় বেদনামথিত
রবীন্দ্রনাথের কবি হৃদয়ের মর্মস্থল থেকে উচ্চারিত হয়েছিল,—
“জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড
অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।”
[নৈবেদ্য;
৬৪ সংখ্যক কবিতা]
আসলে, ধর্ম যদি মনুষ্যত্বের পরিপূরক না হয় তবে,
ধর্ম আর মানবতার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। ধর্মকে সাধনার দ্বারা যদি না অন্তরঙ্গ করে
তুলতে পারা যায়, তবে তা পার্থিব জীবনে মূল্যহীন। সুতরাং জীবনের ধর্ম আর
মন্ত্রবর্ণিত ধর্মের মধ্যে যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে ঔপন্যাসিক তাই বর্ণিত করেছেন।
এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আবুল ফজলের ‘মানবতন্ত্র’ প্রবন্ধের স্থিতধী যুক্তিনিষ্ঠ
মন্তব্যটি স্মরণে আসে। সেখানেও আবুল ফজল মনগড়া মন্ত্র কিম্বা, ধর্মশাস্ত্র আর
জীবনের প্রকৃত ধর্মের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করে বলেছেন;—
“কেতাবের
ইসলাম আর জীবনের ইসলামের মাঝখানে আজ বিরাজ করছে এক প্রশান্ত মহাসাগর।”
আর তাই ঔপন্যাসিক ভবেশ বসুও সমাজের বুকে
চিরশান্তি আর ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তপন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সেলিমকে বুকে জড়িয়ে
ধরে বলেছে,—
“আমার
অন্তরের মাঝে ‘কোরান’ ও ‘গীতা’র থেকেও সত্যও সুন্দর একগুচ্ছ ফুল মালা হতে চাইছে।
আমরা কি পারি না— এক সুতোয় আসতে?”
এ যেন কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই শাশ্বত বাণীর
পুনরোচ্চারণ,—
“মোরা এক বৃন্তে দু’টি কুসুম
হিন্দু-মুসলমান।”
মানুষের মধ্যে যে এত শ্রেণী বিভাজন, এত
ভেদাভেদ-এর মূলে যে মনুর দেওয়া বিধানই দায়ী; সেই সুপ্রাচীন অতীতের দিকেও ঔপন্যাসিক
ভবেশ বসু তাঁর দেবাশিষ চরিত্রের মধ্য দিয়ে ফিরে তাকিয়েছেন। উপন্যাসের কাহিনী
স্রোতে খুঁজে ফিরেছেন—
‘সকল ধর্মের নির্যাস কি?’ তার উত্তরও
ঔপন্যাসিক আপন চেতনার অন্তর্লোকে আলো ফেলে বলেছেন সকল ধর্মের মূল কথা হল— ‘ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস,
আর নিষ্ঠা’। সেই ন্যায় ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে উপন্যাসের জাফেদ যেমন মসজিদে
যায়, তেমনি মন্দিরেও যায়। শুধু ঐ জাফেদ নয়; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘প্রায়শ্চিত্ত’
নাটকের পঞ্চক যেমন সংস্কারের ভয় তুচ্ছ করে পরম কৌতূহল বশত: দীর্ঘ দিনের রুদ্ধ
জানালা খুলে ফেলার সাহস রেখেছিল; তেমনি ঔপন্যাসিক ভবেশ বসুর সৃষ্ট নুরজা নামের
মেয়েটিও নির্দ্বিধায় বলেছে,
“এক
ঘটি জল আর ফুল ও ফল নিয়ে মসজিদে গেলাম। পূজা দিয়ে আবার মন্দিরের ঘট ছুঁয়ে এলাম।
আমার ভীষণ ভাল লাগছিল দাদা।”
এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ‘গোরা’ উপন্যাসের
মহানায়ক গোরার জীবন দর্শনের প্রসঙ্গটিও স্মরণে আসে। যে গোরা এক সময় হিন্দুত্বের
অহংকারে জোলা মুসলমান ঘরের শিশু হিন্দু নাপিতের ঘরে পালিত হতে দেখে, সেই বাড়িতে জল
মাত্র পান না করে ফিরে এসেছিল; আবার সেই গোরাই নিজের জন্ম পরিচয়ে জানে যে, সে আসলে
একজন আইরিশ সন্তান। তখন গোরার ভেতরকার সমস্ত ধর্মের অহং ধুয়ে-মুছে চরম সত্যোপলব্ধি
ঘটেছে। তাই সে সমস্ত ধর্মের ঊর্ধ্বে উদার মানবতার পূজারী পরেশবাবুর কাছেই দীক্ষা
নিয়ে বলেছে, —
“... আপনি
আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান-ব্রহ্ম সকলেরই,
যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনও ব্যক্তির কাছে কোনও দিন অবরুদ্ধ হয় না।
যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন— যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”
আলোচ্য
উপন্যাসে ভবেশ বসুও সেই হিন্দু-মুসলিম এই দুই জাতির ধর্মের বিভাজন চিরতরে মুছে
ফেলতে চেয়েছেন। দুই জাতিকে একই ডোরে বেঁধে দিয়ে সাম্য আর সৌভাতৃত্ব রচনায় সকল
ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে, সুদৃঢ় এক বন্ধনের মাধ্যমে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ
দেখেছেন ও দেখিয়েছেন। আর সেই সৌর্হাদ্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র ‘পথ’ পবিত্র বৈবাহিক
বন্ধন। ঔপন্যাসিক সেই বৈবাহিক বন্ধনের চিত্র রচনায় হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মের
নর-নারীকে একই ঐক্য সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। একদিকে নুরজা আর দেবাশিষ পরস্পরের গলায়
মালা দিয়ে ধর্মের বিভেদ রেখা মুছে ফেলেছে। আবার রোশনাও তপনের গলায় মালা পরিয়ে
দিয়েছে নির্দ্বিধায়। একই ডোরে বাঁধা পড়ে প্রকৃতি-পুরুষ। আবার, জাফেদ বিয়ে করেছে
হিন্দু রমণী মাধুরীকে। এভাবে, কথাশিল্পী ভবেশ বসু জাতীয় সংহতির এক সহজ সমীকরণ
সূত্র উপন্যাসের কাহিনী সূত্রে বাৎলে দিয়েছেন। এই বৈবাহিক বন্ধনের মধ্য দিয়ে
ঐক্যস্থাপন প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক আবুল ফজলের যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্যটি উল্লেখনীয়—
“হিন্দু
মুসলমানের যে কয়টা বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছে তাও এ দৃষ্টিভঙ্গির ফল। এটা মানবতার
দিকের ইঙ্গিত। এমনোভাব বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হলে মিলন ও সহযোগিতার
দিগন্ত বেড়ে যাবে।”
এমন উদার সাম্যরীতির মনোভাব বৃহত্তর সামাজিক
ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হওয়ার লক্ষ্যে, ঔপন্যাসিক ভবেশ বসুর এই শিল্প ফসল ‘মন্দিরে
আজান’ উপন্যাস সৃষ্টি। উপন্যাসের ‘মন্দিরে আজান’ নামকরণের মধ্য দিয়েও সেই সাম্য
চেতনার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। যেখানে মন্দিরে আজান পাঠ হবে আর, মসজিদে শঙ্খ ঘণ্টা
বাজবে, হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মের বাহ্যিক আচার-আচরণ সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে
যাবে। তবেই উভয় জাতির হৃদয়ের সবকটা দ্বার খুলে যাওয়া সম্ভব।
উপন্যাসের
একেবারে শেষ অধ্যায়ে কথাশিল্পী ভবেশ বসু ‘দধীচি’ গ্রামের প্রসঙ্গ এনে পৃথিবীর
কোণায় কোণায় প্রতিটি গ্রামকেই ঐ দধীচি গ্রামের প্রতীকী হিসাবে এনে দাঁড় করিয়েছেন।
যে গ্রামের নারী-শিশু সকলে মিলন যজ্ঞে মেতে উঠেছে। ঔপন্যাসিকের চোখ দিয়ে পাঠক
স্পষ্ট দেখতে পান
“অধিক
উন্নততর জীবন লাভের জন্য মিছিল আসছে।
চলেছে
মানুষ।
শুধুই
মুক্ত মানুষ।
কেউ
আর ভীরু নয়।”
মনের
সমস্ত ভীরুতা ঘুচে গিয়ে—
রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে সকল ধর্মীয় চেতনার ঊর্ধ্বে সাম্যের গান গেয়ে উঠেছে
পৃথিবীর মানুষ। এই চির আশ্বাসের বাণীতে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসের পাতায়
পাতায় কথাশিল্পী ভবেশ বসু অসংখ্য স্থিতধী বক্তব্য রেখেছেন। যে বক্তব্যগুলি মানব
জীবনের চলার পথে অনির্বাণ দীপশিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে শাশ্বত বাণী রূপে। উপন্যাসের
পাতার পর পাতা জুড়ে সেই আলোকোজ্জ্বল বাণীর মধ্য দিয়ে মনের সমস্ত ভীরুতা-জড়তাকে মুছে
ফেলতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। কথাশিল্পীর কাব্যিক চেতনাময় উপলব্ধি পথে ধরা পড়েছে
সমাজ-রাষ্ট্র সম্পর্কে এমন স্থিতধী চিন্তা-চেতনা। ছোট-ছোট সংলাপ আর সুচিন্তিত
বাক্য বিন্যাসে মানবতন্ত্রেরই জয় ঘোষিত হয়েছে ঐ সুদৃঢ় বৈবাহিক বন্ধের মধ্য দিয়ে।
তাই
বলা যায়, অক্ষর শিল্পী ভবেশ বসুর ‘মন্দিরে আজান’ এক অর্থে বিশ্ব মানবের একটি
প্রকাণ্ড সমস্যা মীমাংসার সুচিন্তিত, পবিত্রতম পথ। বৈবাহিক বন্ধন সূত্রে
জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ পিঞ্জর থেকে গণ্ডি অতিক্রমী বিশ্ব মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধতার
পথ। তথা, বিশ্বমানবতা প্রতিষ্ঠারই পথ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ যদি একদিকে
বিশ্বাত্মবোধের উপাসনা ও অপর দিকে ভারত সত্তার পরিচয় হয় তবে, সাম্প্রতিক ঔপন্যাসিক
ভবেশ বসুর ‘মন্দিরে আজান’ও সেই একদিকে বিশ্বসৌভাতৃত্ব বোধ ও অন্য দিকে মানবাত্মার
প্রতিবিম্বন। যে প্রতিবিম্বনে গোটা সমাজের আসল চেহারাটা ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে
জাতীয় সংহতির সহজ সমীকরণের পথ। ‘গোরা’ যেমন রবীন্দ্রনাথের মানস দর্পণ; তেমনি
‘মন্দিরে আজান’ ঔপন্যাসিক ভবেশ বসুর কবি মন তথা, শিল্প মানসের প্রতিবিম্বন। তাই
নজরুলের এক পত্রের অংশ থেকে ভবেশ বসুর এই দুঃসাহসী লেখনী সম্পর্কে বলা যায়—
“আজ
হিন্দু জাতি যে এক নবতম বীর্যবান জাতিতে পরিণত হতে চলেছে, তার কারণ তাদের অসম
সাহসিক সাহিত্যিকদের তীক্ষ্ণ লেখনী।”
গ্রন্থ
ঋণ:
১।
মন্দিরে আজান – ভবেশ বসু, কবিতিকা, ২য় সংস্করণ ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানুষের ধর্ম –
রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ) ১২শ খণ্ড।
৩। নবজাতক – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী
গ্রন্থন বিভাগ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭।
৪। গোরা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী
(সপ্তম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
৫। নজরুল রচনা সম্ভার (প্রথম খণ্ড) ।
৬। চৈতালি – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। পরিশেষ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। নৈবেদ্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯। মানবতন্ত্র – আবুলফজল।