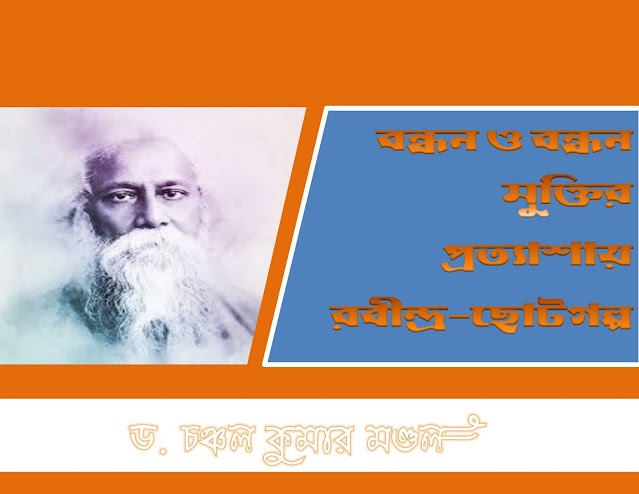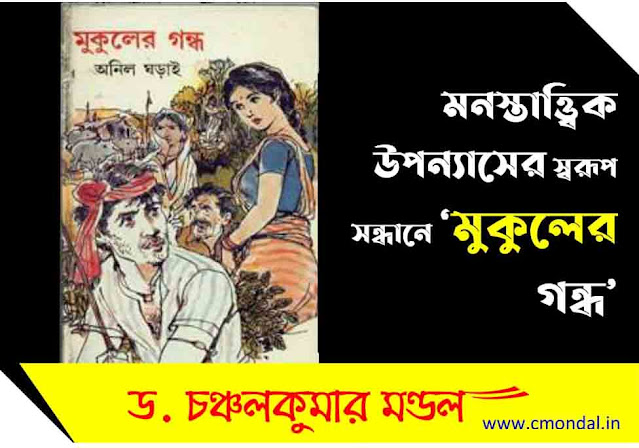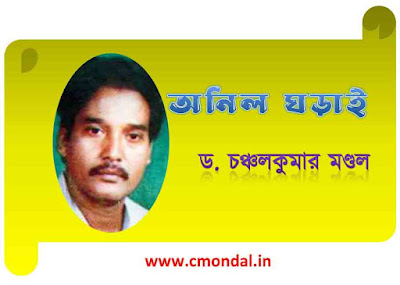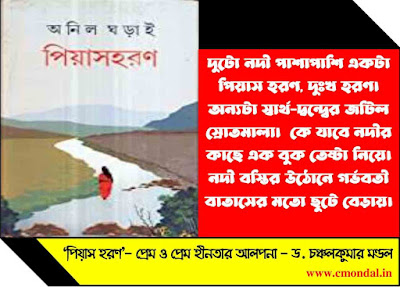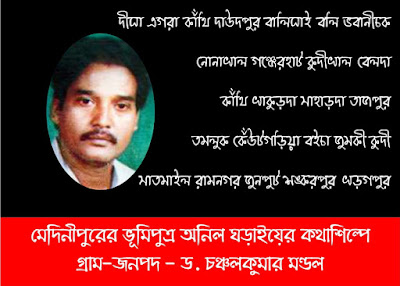বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির প্রত্যাশায় রবীন্দ্র-ছোটগল্প - ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
রবীন্দ্রনাথ যে কেবল অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টি করেছেন তা নয়। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি কলার ভেতরে বহুমুখী প্রতিভার ব্যাপ্তি ও দীপ্তি আমাদের চেতনার মর্মলোকে স্পর্শ করে। এমনকি, তাঁর অজস্র গল্প শৈলীর ভেতরে জগৎ ও জীবনের নানান রহস্য যেমন উদ্ঘাটিত হয়ে উঠেছে; তেমনি নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন ও সেই বন্ধনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পিপাসা জীবন সত্যের গূঢ়তর ব্যঞ্জনায় আভাসিত। কেবল নর-নারীর সম্পর্কের বন্ধন নয়; স্নেহের বন্ধন, প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের বন্ধন ও সেই বন্ধন থেকে মুক্তির পিপাসা রবীন্দ্র-ছোটগল্পের পরতে পরতে আভাসিত। যে গল্পগুলির নিবিড় পাঠে আমাদের মনের রুদ্ধ দুয়ারগুলিও একে-একে খুলে যায়। গল্প-পাঠকও হয়ে ওঠেন বন্ধন পিপাসু, আবার মুক্তিকামী। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের এই বিষয় বৈচিত্র্য এবং নানান আঙ্গিকের অভিনবত্ব সৃষ্টি প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক তাই যথার্থই বলেছেন;
“রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোট গল্প লিখে এক নতুন দ্বীপ আবিষ্কার করেন, জয় করে বিজেতার বীর সম্মানে লালন-পালন শাসন ও করে যান। শাসন অর্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিশীলন, নির্দিষ্ট নীতি-নির্ধারণ। রবীন্দ্রনাথের হাতে যার সগর্ব সূচনা, সেই রবীন্দ্রনাথের হাতেই তার আবার অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি। বিষয়ে বিবিধ রসের স্বাদ সৃষ্টি, পোশাকে বিচিত্র রঙের বাহার দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপাচার সাজানো।”১
সেই বিবিধ উপাচারের ভেতর থেকে কেবল গল্পের তাত্ত্বিক আঙ্গিকে বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির তাৎপর্যতা অন্বেষণ করে দেখা যাক্।
প্রথমেই 'ছুটি' ও 'পোস্টমাস্টার' গল্প দু'টির দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে, ফটিক ও পোস্টমাস্টার উভয়েই বিপরীত পরিবেশ-আত্মীয় বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন নির্বাসন জীবন ভোগ করেছে। ফটিক পল্লী বুকের দামাল শিশু। পল্লী-প্রকৃতির সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক। কিন্তু, সেই সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে নির্বাসিত হতে হয়েছে শহর কলকাতার মত নাগরিক জীবনে। আর পোস্টমাস্টার তো জীবন-জীবিকার তাগিদে শহর জীবন থেকে, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে পল্লীর বুকে এসে বসবাস করতে হয়েছে। পোস্টমাস্টার ঐ পল্লীর বুকে কিশোর রতনের সেবায়, সহচর্যে একটা গভীর হৃদয় বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেছে। গল্প শেষে দেখা যায়, পোস্টমাস্টার রতনের আত্মিক বন্ধন থেকে চাকরি ছেড়ে স্বস্থানে ফিরে গেছে। পল্লীর মুক্ত পরিবেশ তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। রতনের হৃদয়ে বন্ধনও পোস্টমাস্টারকে বেঁধে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। শহরের কৃত্রিম পরিবেশে ফিরে গেছে পোস্টমাস্টার। আর ফটিক নগরজীবনের কৃত্রিম বাতাসে হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই বিচ্ছেদ-বেদনাহত ফটিক অচৈতন্য হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকলে, পুলিশ তাকে ফিরিয়ে আনে। ফটিক পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন থেকে চির মুক্তির প্রার্থনা করেছে- 'মা এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।' অথচ, পোস্টমাস্টারের মধ্যে সেই বন্ধন মুক্তির পিপাসা নেই। পোস্টমাস্টারের ছুটি মেলেনি তার চাকরি জীবন থেকে। বরং তাকে চাকরি ছেড়ে কৃত্রিম নগরজীবনে গা ভাসিয়ে দিতে হয়েছে। পল্লী-প্রকৃতি তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। মুক্ত পল্লী-প্রকৃতি ফেলে বদ্ধ জীবনে ফিরে যেতে হয়েছে। আর, 'ছুটি' গল্পের ফটিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় নিজেই ছুটি চেয়েছে। অথচ, পোস্টমাস্টার রতনের হৃদয় বন্ধন ছিন্ন করে ফিরে যাওয়ার যন্ত্রণা ঢাকতে নিজেকে কেবল সান্ত্বনা দিয়ে দার্শনিকতার সুরে মনে-মনে বলেছে; 'পৃথিবীতে কে কাহার!' আর ঐ হতভাগী কিশোরী রতন, সে তো হৃদয় বন্ধনে আটকা পড়ে পোস্ট অফিসের চারপাশে কেবল ঘুরে বেড়িয়েছে। তার আশা মরেনি। বন্ধন ডোরে বন্দী থেকে রতন পথ চেয়ে থেকেছে; 'যদি দাদাবাবু ফিরিয়া আসে!'
এভাবে, রবীন্দ্রনাথ 'বন্ধন ও বন্ধন মুক্তি'র প্রত্যাশায় নর-নারীর স্নেহ-প্রেম, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ ছবি এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। তাই কবি মনের অভিপ্রায় হিসেবে 'বন্ধন ও বন্ধন মুক্তি'র তাত্ত্বিকতায় 'সোনার তরী' কাব্যে লিখেছেন -
"বন্ধন? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহ প্রেম সুখ তৃষ্ণা, সে যে মাতৃ পলি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইতেছে পান।" [‘সোনার তরী’ : ‘বন্ধন’]
এইরূপ 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের ভেতর লক্ষ্য করা যায় পিতৃহৃদয়ে গভীর বাৎসল্য প্রীতির দরুন অপার স্নেহের বন্ধন রচনা করেছেন গল্প শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। শহুরে শিক্ষিত নাগরিক জীবনের আবহে গড়ে ওঠা পিতৃ হৃদয়ের সঙ্গে ঐ অশিক্ষিত খুনি কাবুলিওয়ালার পিতৃ হৃদয়ের কোন প্রভেদ নেই। হৃদয় বন্ধনে উভয় পিতা-ই এক। এই গল্পের 'বন্ধন ও বন্ধন মুক্তি'র প্রত্যাশা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট রবীন্দ্র গল্প সমালোচক 'সোনার তরী'র বিখ্যাত একটি কবিতার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন -
“কাবুলিওয়ালা গল্পটির সঙ্গে 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির মর্মগত মিল অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। দু'ই রচনাতেই শিশু কন্যার প্রভাবে অভ্যাসের জড়তা হইতে পিতৃমন মুক্তি পাইয়াছে।”২
পূর্বোক্ত 'ছুটি' গল্পের ফটিকের সগোত্রীয় 'সুভা' গল্পের সুভা ও 'সমাপ্তি' গল্পের মৃন্ময়ী। এরা তিনজনেই প্রকৃতির সঙ্গে একই যোগসূত্রের বাধা পড়েছে। স্বামী প্রেম উপলব্ধির জন্য মৃন্ময়ীর মধ্যে বিচ্ছেদের প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন ছিল। যে আঘাতে মৃন্ময়ী মাটির বন্ধন মুক্ত হয়ে স্বামীর বাহুবন্ধনে ধরা দিতে পেরেছে। আর, ঐ সুভাকে প্রকৃতির বন্ধন ছিন্ন করে বিবাহসূত্রে শহুরে জীবনে এনে ফেললে মুক্তি পিপাসুরা সংসারের নিষ্ঠুর আঘাতে নিঃসঙ্গ একাকিনী হয়ে ওঠে। শকুন্তলার মতো স্বামী প্রত্যাখ্যাতা মুক বালিকা সুভারও 'ছুটি' গল্পের ফটিকের মত মুক্তি একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই রূপ 'অতিথি' গল্পের তারাপদ বন্ধন মুক্তির পিপাসায় 'সোনার তরী' কাব্যের 'দুই পাখি' কবিতার বনের পাখির মুক্তির সোল্লাস স্মরণ করিয়ে দেয়। কিশোর তারাপদকে স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের বন্ধনে চার দিক থেকে বেঁধে ফেলবার পূর্বেই, সারা গ্রামের হৃদয় চুরি করে এক বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে সে বিশ্ব-জননীর কোলে আশ্রয় নিয়েছে। তারাপদর মনে একমাত্র সংশয় ছিল, পাছে ঐ বন্ধনে বাঁধা পড়ে যায়। খাঁচার পাখিকে দেখে তার মনে কেবল সংশয় উদ্রেক করেছে; 'কবে খাঁচায় রুধি দিবে দার।' এমনকি, 'বলাই' গল্পে দেখা যায় পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসঙ্গ জীবনে বালক বলাই উদ্ভিদের সঙ্গে সখ্যতার বন্ধন রচনা করেছে। বৃক্ষ জীবনের সঙ্গে মানব জীবনের নিবিড় বন্ধনলীলা রবীন্দ্রনাথ এই গল্প রচনার পর 'বনবাণী' কাব্যে সেই ভাব 'জগদীশচন্দ্র' নামক কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।
আবার, সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন 'হৈমন্তী' ও 'দেনাপাওনা'র মতো গল্প। এই গল্প দ্বয়ে নারীকে পণ্য হিসেবে কেনাবেচার মত পণপ্রথা নামক ঘৃণ্য সংস্কারের বন্ধন থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির তাত্ত্বিক ভাবনায় 'একরাত্রি' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত বিরহের ছবি এঁকেছেন। যে সুরবালার প্রেমের বন্ধনকে এক সময় অস্বীকার করে দেশোদ্ধারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নায়ক; সেই নায়কের স্বপ্নের মোহ ঘুচে গিয়ে সুরবালাকে না পাওয়ার বেদনায়, অনুশোচনায়, ব্যর্থতা, পরাজয়ের গ্লানিতে হাহাকার করে মাথা কুটে মরেছে। আজ পরঘরনী সেই সুরবালার সাথে প্রেমের বন্ধনে বাধা পড়ার ব্যর্থ স্বপ্নে বিভোর নায়ক। 'ব্যর্থ স্বপ্ন' কারণ, তার সুরবালা এতদিনে রামলোচনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে বন্দী। ব্যর্থ নায়ক আজ 'বাঁশি' কবিতার হরিপদ কেরানির মত একরাত্রির জন্য মোহের বন্ধনে আটকা পড়ে সুরবালার সঙ্গে স্বপ্নালোকে মিলিত হয়েছে। এ যেন হরিপদ কেরানির আক্ষেপ, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থ সান্ত্বনা -
“ঘরেতে এল না সে তো
মনে তার নিত্য যাওয়া আসা।” [‘পুনশ্চ’ : ‘বাঁশি’]
এই গল্পের বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির তত্ত্বভাবনা 'সোনার তরী'র 'পরশপাথর' ও 'আকাশের চাঁদ' কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'গল্পগুচ্ছে'র সমালোচনায় এই গল্পের নায়কের মোহবদ্ধ জীবনের মুক্তির প্রসঙ্গে, তাই যথার্থই পৌরাণিক উপমায় সমালোচক বলেছেন:
“একরাত্রি' গল্পের সেই আপাত ভয়ঙ্কর রাত্রি - বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের মোহমুক্তির মতই নায়কের মোহের বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছে। তাকে দিয়ে শাশ্বত পথের নিশানা। নায়ক এক অনির্বচনীয় ভাব তন্ময়তায় জীবন-মৃত্যুর শাশ্বত মর্মবাণীকে উপলব্ধি করেছে, তার অস্থির মানসিকতা, কাল্পনিক স্বপ্নচারিতা ও অন্তর্প্রক্ষোভের উপশম ঘটেছে।”৩
আবার 'গুপ্তধন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ মোহের বন্ধন ও সেই বন্ধন মুক্তির তাত্ত্বিক ছবি এঁকেছেন, মৃত্যুঞ্জয় ও বনোয়ারীলাল উভয়ের অর্থাকাঙ্ক্ষার প্রভেদ রচনার মধ্য দিয়ে।
অবশেষে, 'বন্ধন ও বন্ধন মুক্তি'র প্রত্যাশা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির, নারীর স্বাধীকার বোধ প্রতিষ্ঠার যে ছবি এঁকেছেন, সেই প্রসঙ্গে আসা যাক্। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনী নারীত্বে, সতীত্বে, মাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধা এক ব্যক্তিত্বময়ী রমণী। যাকে পত্নীত্বের বন্ধনে বেঁধে নন্দকিশোরের স্বপ্ন পূর্ণতা পেয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পর সোহিনী ল্যাবরেটরিকে রক্ষার জন্য সমাজ-সংস্কারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বৈজ্ঞানিককেও মোহের বন্ধনে বেঁধে রাখতে দ্বিধা মাত্র করেনি। আবার, 'শাস্তি' গল্পের চন্দরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। চন্দরাকে তার স্বামী একরকম জোর পূর্বক মিথ্যা খুনের দায় চাপিয়ে দিতে চেয়েছে এইভাবে যে; - 'বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইবো না।' পত্নী সম্পর্কে স্বামীর এমন উদাসীনতায়, স্বামীর হঠকারী সিদ্ধান্তে চন্দরার নারীত্বে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তাই অভিমানহতা চন্দরা ইহজীবনের শেষ বন্ধন হিসেবে ফাঁসির দড়িকেই নীরবে বরণ করে নিয়েছে। স্বামীর প্রতি ক্ষোভ-অভিমানে প্রেমের বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হয়ে গেছে। 'কঙ্কাল' ও 'নিশীথে' গল্পেও এমনই প্রেম বঞ্চিতা নারী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির পথ বেছে নিয়েছে। আর ওই চন্দরা তো টলস্টয়ের আন্নার মত সংকল্প ঘন চিত্তে মুক্তিকামী হয়ে উঠে স্বামীর সঙ্গে ইহজীবনের বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়ে বলেছে, 'আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নব যৌবন লইয়া ফাঁসি কাঠকে বরণ করিলাম - আমার ইহজন্মের শেষ বন্ধন তাহার সহিত।' এভাবে, স্বামী ছিদামের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চন্দরা ফাঁসি কাঠকেই বরণ করে নিয়েছে। ফাঁকি কাঠই তার মুক্তির শেষ আশ্রয়। আর তাই সিভিল সার্জন তাকে ফাঁসির পূর্বমুহূর্তে স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখা করার কথা বললে, বেদনাহত চিত্তে চন্দরা কেবল উচ্চারণ করেছে 'মরণ'। ঐ একটি মাত্র শব্দেই সমস্ত নারী সমাজের হয়ে চন্দরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতি ঘৃণা ছুড়ে দিয়েছে।
'স্ত্রীরপত্র' গল্প পাঠে মধুসূদন দত্তের নারীমুক্তির মুখপাত্র 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কথা স্মরণে আসে। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারী মুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারী মৃণাল বাঁধাধরা জীবনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। বৃহৎ বিশ্ব-লোকের আহ্বানে সে সাতাশ নম্বর মাখন বড়াল লেনের গলির বদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। মৃণালের এই বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কবির 'পলাতকা' কাব্যের 'মুক্তি' কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। মৃণাল কেবল মেজো বউ হয়ে বাঁচতে চায়নি। তার বাঁচা পত্নীত্বে নয়, নারীত্বে। তাই সে পুরুষের শ্রীচরণতলাশ্রয় ছিন্ন করার স্পর্ধায় মুক্তির বাণী বহন করেছে। মেজো বউ-এর খোলস ছিন্ন করে তাই বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে মৃণাল বলেছে; -
"আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভাল লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে দেখেছেন। এইবার মরেছে মেজো বউ।...আমি বললুম।"
মৃণালের এই বেঁচে ওঠা অর্থে, বন্দী জীবন (মৃত, জড় জীবন) থেকে মুক্তি পাওয়ার অনাবিল আনন্দ। রবীন্দ্র-ছোটগল্পের প্রাজ্ঞ-স্থিতধী সমালোচক এ প্রসঙ্গে তাই যথার্থই বলেছেন, -
"মেজোবউ মরিয়া নারী রূপে নূতন জন্মলাভ করিল। এ আনন্দ মুক্তির, এ বাঁচা নারী জীবনের সার্থকতার।"৪
এভাবে, রবীন্দ্র ছোটগল্পের পর্বে পর্বে বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির বিচিত্র সব তাত্ত্বিক ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। যেগুলি তাঁর কবি মনের অভিপ্রায় হিসেবে বিভিন্ন কবিতায়ও সেই তাত্ত্বিক ভাবনাগুলি বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির বাণী রূপ লাভ করেছে। তাই কবির বিভিন্ন ছোটগল্পের সঙ্গে এভাবে কবিতার ভাব সামঞ্জস্য পাশাপাশি তুলে ধরলে দেখা যাবে নর-নারীর বিচিত্র বন্ধনলীলা ও সেই বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্র-শিল্প মানসের অভিব্যপ্তি অত্যন্ত তাৎপর্যময়। আর এই ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'শেষসপ্তক' কাব্যের বিয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতার মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটি ছত্র তুলে ধরে এ প্রসঙ্গে যবনিকা টানা যায় -
"মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,
যে-মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখ দুঃখের দুর্গম পথে,
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়;"
সেই সকল চলমান মানুষের বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির লীলা-চিত্র রবীন্দ্র-গল্প শিল্পে সুগভীর তাৎপর্যতায় ফুটে উঠেছে।
তথ্যসূত্র:
১। “বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ” (১ম খণ্ড) - ধীরেন্দ্র দত্ত, এস-পি পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৪০৭, পৃ. – ১৪।
২। “রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প” - প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা – ৭৩, নবম মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪০০, পৃ. – ৪৯।
৩। “গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ” - সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা - ০৯, পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১১, পৃ. – ৯৪।
৪। “রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প”, প্রাগুক্ত, পৃ. – ৬৪।
লেখক পরিচিতি:
ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল, এস. এ. সি. টি. – ১, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিক, আধুনিক কথাসাহিত্যিকে অনিল ঘড়াই-এর সম্পূর্ণ জীবন ও শিল্প কলা নিয়ে পি-এইচ. ডি. উপাধি সহ সাহিত্যিক হিসাবে একাধিক পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী।