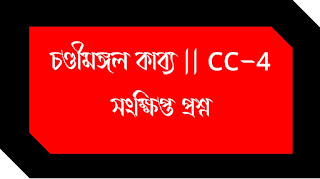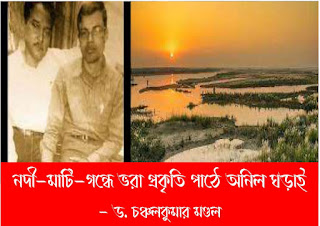জীবন-সাধক অনিল ঘড়াই
দলিত সাহিত্যের এক সার্থক তূর্যবাদক অনিল ঘড়াই। তিনি কেবল দলিত সাহিত্যিক হিসেবেই নন, একজন অত্যন্ত সহৃদয় নিষ্ঠ-প্রগাঢ় জীবনঘনিষ্ঠ সুসাহিত্যিক হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার আজীবন সাহিত্য সাধনায়। ফলে, অশ্রু আর শ্রমঘামে সিক্ত-বেদনার গাঢ়রসে রঞ্জিত, মাটি-মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যা সংকটের ছবির ভেতর দিয়ে জীবন সম্পর্কে নব-নব ভাবনা বিকশিত করে তুলেছেন। লোকায়ত দর্শনলব্ধ শিল্পীমনের ভেতর দিয়ে ধরা পড়েছে জীবন সম্পর্কে এক গভীর-অভাবনীয় সত্যতার সুলুক সন্ধান। আসলে—
অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের পরও মানুষ আরও কিছু চায়।
সেই আরও চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকেই খোঁজার চেষ্টায় তিনি জীবনের অমোঘ বাস্তবতা কেই সহজে স্বীকার করে নিয়েছেন। জীবন-বাস্তবতায় কোনো মিথ্যা কিম্বা ছলা-কলার সামান্যতমও আশ্রয় নেননি।
এই মেদিনীপুরের প্রান্তিক প্রদেশে তার জন্ম (এগরার রুক্মিনীপুর গ্রামে ১লা নভেম্বর ১৯৫৭)। কিন্তু জীবনে-জীবিকার তাগিদে জন্মভিটে ছেড়ে পিতার হাত ধরে একসময় পাড়ি দিতে হয় ভিনজেলা তথা নদীয়ার কালীগঞ্জে। জীবনের অনেকটা সময় তার কেটেছে বিলঘেরা বুনোপাড়ায়। আবার, আপন কর্ম রেলওয়ের চাকরির সুবাদে বাংলা-বিহারের অগুনতি প্রান্তিক জনজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ মিলেছে। অতি কাছ থেকে শ্রমমুখর-ঘর্মক্লান্ত মানুষের জটিল-কঠিন যাপন-পদ্ধতি হৃদয় দিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে, ঐ মানবজীবনের প্রতি শিল্পীহৃদয়ের অপার সহমর্মিতা ও ফেলে আসা সেই শৈশব-কৈশোরের চারপাশের চির অভাবীপূর্ণ মানুষজনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ছবির ভেতর দিয়ে সাহিত্যে শিল্পীত রূপ পেতে থাকল। যে কারণেই তার প্রতিটি কথাকলা আত্মজৈবনিক উপাদানে ভরে উঠেছে। শেকড় উপড়ানো বিলাঞ্চলের ভূমিহীন নর-নারীর দিন যাপনের গ্লানিকর মুহূর্তগুলি নান্দনিকতায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করার মতো।
পারুল ফুলের পোশাক পরে চলেছে ফুলের দেশে।
কিম্বা—
ভেজানো দরজা খুলে সে দেখল ধীরপায়ে তার ঘরের দাওয়া থেকে নেমে উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সরসী। মরা চাঁদের মতো চেহারা তার। হাওয়ায় উড়ছিল খোঁসাভাঙা চুল। পিছন থেকে তাকে মনে হল বিসর্জনের প্রতিমা।
এমন অসহায় সমাজলাঞ্ছিতা নারী সমাজের আর্তরোল, অনিল ঘড়াইয়ের মতো গল্পকারের দরদী লেখনীস্পর্শে বাস্তব সত্যরূপে ধরা পড়েছে। গল্পের কনক, ঝর্না, মালতি, বিনতিরা, পারুলের মতো দেহপসারিণী হতে বাধ্য হওয়া নারীদের সমাজ কতটা ঘৃণা করে, অবাঞ্ছিত রূপে দূরে সরিয়ে রাখে তারই বেদনাকাতর ছবি এই গল্পে ফুটে উঠেছে। পারুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা গেলে কেউ তার শবদেহ সৎকারে হাত লাগাল না। তাই শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে বস্তির অনন্য দেহপসারিণী নারীরা তাদের জীবিকা সঙ্গী পারুলের শবদেহ সৎকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অথচ বস্তিতে সেদিন লেংটা কার্তিকের পুজো’ নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে দেহ পসারিণীদের যৌন ব্যবসায় নামার দিন। পথের দুপক্ষের লোকজন ওদের দেখে অবাক বিস্ময়ে—
ওদের চোখেমুখে হতাশা কিংবা
পরাজয়ের কোন চিহ্ন নেই বরং ওরা হেমন্তের
ভোরে ফোটা ফুলের চেয়েও স্বচ্ছ, তরতাজা।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসের অন্যতম ট্রাজিক জীবনের নায়িকা দেহপসারিণী বসনের মৃত্যুতেও এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। বসনের মৃত্যুর পর মাসী তার গা থেকে অলঙ্কারগুলি খুলে নেয়। তারপর তার সকারের কাজে বসনের প্রেমিক হিসেবে নিতাই কবিয়াল ছাড়া কোনো পুরুষকেই ঐ শ্মশানযাত্রায় দেখা যায়নি।
এভাবে নারী জীবনের ব্যর্থতা হাহাকারের নির্মম অতি মর্মন্তুদ ছবি, অনিল ঘড়াইয়ের অত্যন্ত দরদী লেখনীতে সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। দলিত সাহিত্য সহানুভূতি চায় না—চায় সমানুভূতি হতে চায় প্রবল আন্তরিকতা। সেই আন্তরিকতা, সমানুভূতি অনিল ঘড়াইয়ের মধ্যে পুরােমাত্রায় ছিল। যা তার প্রতিটি শিল্প প্রকরণে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন। সে কারণেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, দূর থেকে দেখা গ্রাম জীবনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তারাশঙ্কর হওয়া যায় না— মহাশ্বেতা দেবী হওয়া তো অনেক দূরের কথা। আবার সমরেশ বস, অদ্বৈতমল্ল বর্মণদের মতো প্রান্তিক গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনঅভিজ্ঞতার জ্বলন্ত ছবিগুলি উঠে এলেও, গোটা ভারতবর্ষীয়—এমনকি, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়েও এমন ব্যাপকতর দলিত জীবন অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন মাত্র করে জীবনের ঐ আসল ঐশ্বর্যকে ছোঁয়ার সাধনায় অনিল ঘড়াই হতে পেরেছেন ক'জন? কারণ, অনিল ঘড়াই হওয়া? সে তো অনেক, অনেক কঠিনতর সাধনার ব্যাপার!
জীবনভাবনা / দর্শন
তাই তাঁর, ‘নাগর’ গল্পে দেখা যায়, রসের নাগর সুধাদাসের মধ্য দিয়ে জীবনকে খুঁজে ফেরার শিল্পী হৃদয়ের কি দুর্বার মোহময় আকাঙ্ক্ষা। জীবনের নয়, জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তিতেই ভিটেমাটি হারা খালপাড়ের ভিক্ষবৃত্তিধারি মানুষ সুধাদাস চরিত্রের ভেতর দিয়েই শিল্পীমন ছুঁতে চেয়েছেন জীবনকে। সুধাদাসের গাওয়া গানের ভেতর দিয়ে জীবনকে না বুঝে উঠতে পাহাড় খেদোক্তি, যা শিল্পী হৃদয়েরই আর্তি রূপে ফুটে ওঠে; যখন সুধাদাস গেয়ে ওঠে—
জীবনের কুননা শিকড়া পেলাম না।
জীবন হল নীলদরিয়ার ছোট্ট সেই ডিঙা,
তলাফুটা পচা কাঠের ডিঙা।
জীবনের কুনো তল পেলাম না।
জীবন তো নোনা খালের ধুলা
মন চলরে একলা!
এমনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসে নায়ক নিতাই কবিয়ালের জীবন থেকে দু-দুটো ভালোবাসার নারী (ঠাকুরঝি ও বসন) হারিয়ে গেলে, পদম খোদাক্তিতে নিতাই কবিয়ালও ঐ আলোচ্য ‘নাগর’ গল্পের নায়ক সুধাদাসের মতন জীবন সম্পর্কে গেয়ে উঠেছে—
এই খেদ মোর রহিল মনে
ভালোবেসে মিটল না সাধ
কুলাল না এ জীবনে—
হায়! জীবন এত ছোটো কেনে!—
শিল্পী অনিল ঘড়াইয়ের কথাশিল্পের অক্ষরে অক্ষরে লেগে রয়েছে সেই জীবনের স্পন্দন। জীবনকে চেটেপুটে পরখ করার প্রবল আসক্তি। তাঁর প্রতিটি কথাশিল্পের মতো এই ‘গানের’ গল্পের মধ্যেও তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর মেলে। যখন, স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারী খেরির সংস্পর্শে আসথে চায় সুধাদাস, তখন খেরির মুখ দিয়ে সুধাদাসকে বাঁধ দিতে বলে। এ বাঁধ সংযমের বাঁধ। শিল্পী অনিল ঘড়াই লক্ষ্য করেন জীবনের ভেতর আরেক জীবন। তাই খেরির মুখ দিয়েই তিনি বলেন—
সব মানুষের ভেতর একটা নদী বয়।
যে নদীতে ভাঁটার চেয়েও জোয়ার বেশি।
এভাবে ঐ খালপাড়ের দুটি ছিন্নমূল নর-নারীর কুলহারা জীবন দুটো—যেভাবে রম্পরকে বুঝতে চেয়েছে, সেই বোঝার চেষ্টার ভেতর দিয়ে শিল্পীমনের জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে। যখন ঐ খেরি সুধাদাসকে বলে—
আমি তুমারে ঠিক বুঝতে পারিনে।
—এই প্রশ্নের উত্তরে দাসের মুখ দিয়ে শিল্পীমনের জীবন সম্পর্কে সেই জিজ্ঞাসা—
‘আজ অব্দি কেউ তো কাউরে বোঝোনি।
কেবলই বোঝার ভাণ। এই যে নোনাখাল
অতবড় সমুদ্র কি তারে বঝে?
জীবনকে এই বোঝার, জানার কোনো শেষ নেই। তাই তো যুগে-যুগে কত মহাজ্ঞানী, শিল্পী সুফীসাধক, আউল-বাউল থেকে যোগী, মুনি-সুফীগণ জীবনের ঐ ‘তল’ খুঁজে ফিরেছেন। শিল্পী অনিল ঘড়াইয়ের কাব্যবীণায়ও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে সেই সুর—
‘জীবনেরও আছে তল’। কিন্তু, অনুভব মাত্র। কিন্তু, সেই তল’ ছোঁয়ার সাধ্য কার? কারণ—
জীবন? সে-তো নীলদরিয়ার
উথাল-পাথাল ঢেউ, ।
শুধু, উপর-উপর ঢেউ ভাঙে তার
‘তল’ পায় না কেউ!
সেই ‘তল’ খোঁজার প্রসঙ্গে কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছিলেন,
বাহিরের ঐ মন্থনের ফলে, যে বিপুল ফেনারাশি উৎপন্ন হয়, তাহার বুদবুদ জলের অন্তর নাই! সেই জাল ছিন্ন করিয়া তাহার তলদেশের শান্ত-স্বচ্ছ নীলশোভা যিনি দেখিতে ও দেখাইতে পারেন তিনিই জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপকার।
লোকায়ত জীবনভাবনায় অনিল ঘড়াইয়ে ঋদ্ধ অনিল ঘড়াইয়ের শিল্পচিন্তায় জীবন ঐ নিত্যদিনার ঘটে যাওয়া ঘটনার ঘনঘটায় মন্থনজাত বুদবুদ জাল ছিন্ন করে, তার অন্দরমহলে আলো ফেলে জীবনকে দেখার ও দেখাইবার কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! যা, তাঁর কি কাব্য শিল্প, কি কথাসাহিত্যের পরতে-পরতে লক্ষ্য করার মতো। তাই এই ‘নাগর’ গল্পের অসহায় নারী খেরির অকালমৃত্যুতে সুধাদাসের অনুভবে, জীবন সম্পর্কে ধরা পড়ে—জীবন যেন ছিল পিছলান তীর, বা আরো কিছু। সুধাদাসের ভেতর দিয়ে শিল্পীহৃদয়েরই খেদোক্তি—
মানুষ জীবনের রহস্য তার জানা হল না।
মনে হয় জীবন একটা বিশাল আকাশ।
সেই আকাশের তলে বষে তারাশঙ্করের সতীশ ডোম তরফে নিতাই কবিয়ালের মতো অনিল ঘড়াইয়ের সৃষ্ট জীবন রসের রসিক সুধাদাস জীবনকে জানার অনন্ত পিপাসায় গেয়ে ওঠে;
জীবনরে তোর তল খুঁজে পেলাম না!
অনিল ঘড়াইয়ের কথাশিল্পের অক্ষরে-অক্ষরে জীবনানুভবের জীবনবোধের গাঢ়তা নবনব ভাবরসের সুললিত বর্ণনায় আস্বাদনপন্থী হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণবল্লভা রাধা আক্ষেপ করে বলেছিলেন—
‘আমার প্রতি রোম যদি চক্ষু হইত,
তাহা হইলে সাধ মিটাইয়া শ্যামরূপ
দেখিতাম।
বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ অনিল ঘড়াইয়ের শিল্পীমনও ঐ রাধার মতো অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে জীবনকে দেখার এমনই অন্তহীন আকুলতায় জীবনভাবনা অথচ মানবভাবনা শিল্পচেতনায় প্রকট হয়ে উঠেছে। যেখানে ঐ দলিত জীবনে রুটির লড়াইয়ের সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে গ্রথিত করে শিল্পী মানবকল্যাণে নিজেকে উৎসারিত করে দিয়েছেন। এই দুরূহ কাজ সকলেই পারেন না; সম্ভবও নয়। কারণ, শিল্পীর নিজস্ব কাব্য-কথায় একমাত্র সেই পারেন;
কাদাজল সংসারে শ্যাওলা সরিয়ে যে কাটে সাঁতার
ডুব দিয়ে সে খোঁজে জীবনের আসল ঐশ্বর্য।
কারণ, গ্রাম-জীবনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে দলিত সাহিত্য রচনা করা যায় না। সেই অভিজ্ঞতা যদি চিন্তাযুক্ত না হয়। তাই, আবার বলি দূর থেকে দেখা দলিত জীবনের অভিজ্ঞতাকে মালমশলা করে বড়জোর মাকি বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও হয়তো হওয়া যেতে পারে, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবী হওয়া যায় না। অনিল ঘড়াই তো হওয়া আরো কঠিন। আসলে, নগর জীবনের আভিজ্যাতের আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে ঐ অন্ত্যজ জীবনের দৈনন্দিন যাপন পদ্ধতি অতি কাছ থেকে, ঐ জীবন মাঝে মিশে গিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। কথাশিল্পী অনিল ঘড়াই ঐ জীবনের শরিক হিসেবে, ঐ জীবনের পদরজ করপুটে অঞ্জলি করে স্পর্শ পেয়েছেন শাশ্বত মানবতাবাদের। অস্তেবাসী নর-নারীর জীবনপটেই (হৃদয়পটেও) তিনি খুঁজে ফিরেছেন জীবনের প্রকৃত মানে। জীবন উপভোগ করার বিচিত্র সব অভিনব কৌশলের মধ্যে দেখা যায় জীবনকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখার শিল্পীমনের কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। ঐসব ছেঁড়া-খোঁড়া, নাঙ্গা, লাঞ্ছিত মানব জীবনকে গভীরভাবে ভালোবেসে, ঐ জীবনেরই মাঝে তিনি লাভ করালেন প্রকৃত মানবতার দর্শন।
সুতরং বিষন্ন বেদনামথিত বৃহত্তর ঐ প্রান্তিক জীবনের সিন্ধুতটে উপনীত হয়ে শিল্পীহদয়ের মহত্তর অনুভূতিতে দেশ-কালের সীমা অতিক্রমকারী জগৎ-জীবনের যে অতি মরমীঘন ছবি একের পর এক এঁকে গেছেন, তার স্বরূপ কেবল পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে অনুভব করা যায় না। সেই বিচারের দাবী তোলা রইল মহাকালের দরবারে, কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে ওঠার অপেক্ষায়।
তবু বলতেই হয়, জীবন সম্পর্কে সহানুভূতিময় এমন সব মহানুভব-মহানুভূতি, শিল্পীর নিজস্ব বাকরীতি নির্মাণের অতি সাবধানী শিল্পচেতনায় প্রকট হয়ে উঠেছে, যা তার একান্ত নিজস্ব সুর ও স্বরের সেতারের বহুরাগিনীর তারে বাঁধা।
----ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল