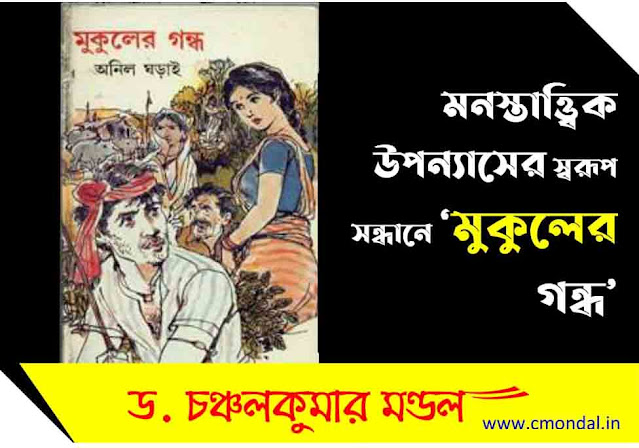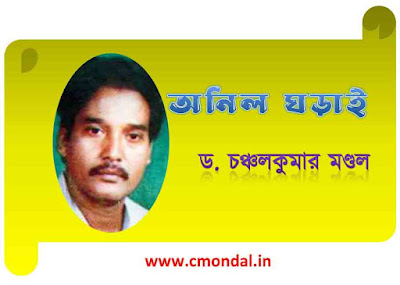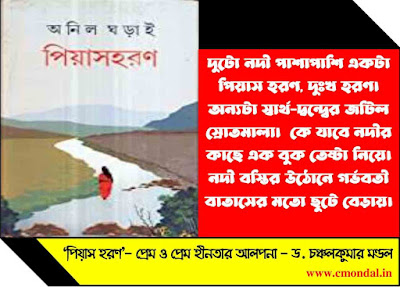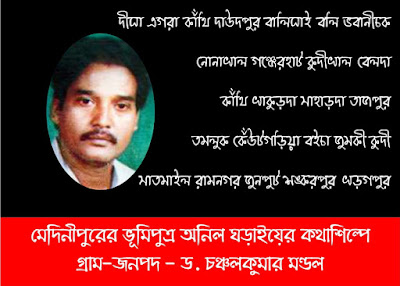পোস্টমাস্টার : বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশায় - ড. চঞ্চল কুমার মণ্ডল
রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাই কবিমনের অভিপ্রায় হিসেবে কথাশিল্পের মধ্যেও নানান তত্ত্ব রূপায়িত হয়েছে। সেইরূপ তাঁর ছোটোগল্পের কাহিনিপটে নর-নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য-বেদনা, মিলন-বিরহ-বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বন্ধন ও বন্ধন মুক্তির তত্ত্বকথা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাবাহিতা লাভ করেছে। মানবজীবনের নানান জড়তা-মূঢ়তা সংস্কারে বন্ধন থেকে তিনি যেমন মুক্তির প্রার্থনা করেছেন, তেমনই জীবনের স্নেহ-প্রেম, মানবিকতার বন্ধনকে সত্য হিসেবে সহজে স্বীকার করে নেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর গল্পভাষায় নারী-পুরুষের অন্তর্বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা আবেগ-উৎকণ্ঠাকে তিনি বন্ধন-মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন। আসলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পশিল্পের ভিতর দিয়েও নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যেমন স্নেহ-প্রেমের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে প্রচণ্ড আঘাতে (মৃত্যুর বেদনায়) ঐ সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করছিলেন। খুঁজে ফিরেছেন, বন্ধনমুক্তির, চিরপ্রশান্তির পথ। তেমনই সেই বন্ধন ছিন্ন করার প্রত্যাশা তাঁর শিল্পীমনের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল।
অকালে পত্নী বিয়োগ, সন্তানকে হারানোর যে অসহনীয় যন্ত্রণা; সেই যন্ত্রণা থেকে বিচ্ছেদের হাহাকার থেকে কবি মুক্তির পথ খুঁজে ফিরেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও কবি, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক, প্রথাগত শিক্ষায় বিশ্বাসী নন। দমবন্ধ-করা, ইট-কাঠ-ঘেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি বিদ্রূপ হেনেছেন। আর তারই প্রতিবাদ তথা, বন্ধন ছিন্ন করার প্রতিবাদে লিখেছেন ‘তোতা কাহিনী’-র মতো তীব্র শ্লেষাত্মক গল্প। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে গিয়ে মুক্তিকামী রবীন্দ্রনাথ তাই মুক্ত শিক্ষাঙ্গন হিসাবে গড়ে তুলেছেন ‘শান্তিনিকেতন’। এই নিবিড় ছায়া সুশীতল অরণ্যে-ঘেরা মুক্ত প্রকৃতির কোলে গড়ে-ওঠা শান্তির আশ্রয় ‘শ্রীনিকেতন’-ই হল কবির মুক্ত শিক্ষাঙ্গন। এভাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি শিল্প প্রকরণের ভিতর দিয়ে সেই বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশা নানা তত্ত্বকথায় উপস্থাপিত হয়েছে।
গল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শোষণরূপ শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘোষণা করেছেন, নারী মৃণাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নগরজীবনের যন্ত্রবদ্ধ জীবন থেকে চিরতরে মুক্তি চেয়েছে ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক। প্রকৃতির কন্যা সুভা ও নিয়মবদ্ধ সংসারের চড়ায় আটকে গিয়ে বাঁধা পড়তে চায়নি। তাই সে বার বার মুক্তির প্রত্যাশায় ছুটে গেছে প্রকৃতির কোলে। এভাবে ‘সুভা’ গল্পের কিশোরী সুভা-সহ ‘অতিথি’-র তারাপদরা বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশায় ডানা-ভাঙা পাখির মতো ছটফট করে, মাথাকুটে মরেছে। এমনকী কবির ‘গুপ্তধন’ গল্পেও দেখা যায়, মোহমুক্তির তত্ত্বকথা রূপায়িত হয়েছে। তেমনই, আলোচ্য ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পের যে স্নেহ-প্রেমের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির নিদারুণ-নিষ্করুণ যন্ত্রণা রূপায়িত হয়েছে; তাতে কবিমনের তত্ত্বকথা রূপায়িত হয়েছে। এই গল্পের বন্ধনও বন্ধনমুক্তির নির্মম-নিষ্ঠুর প্রতিচিত্রণ তুলে ধরার পূর্বে কবির ‘সোনার তরী’ কব্যের ‘বন্ধন’ কবিতাটির কথা একবার স্মরণ করে নেওয়া যাক —
বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন
স্নেহ-প্রেম-সুখ-তৃষ্ণা, সে যে মাতৃপলি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসস্রোতে পূর্ণ করিমন
সদা করাইতেছে পান।’১ (‘সোনার তরী’/ ‘বন্ধন’)
আলোচ্য ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে রতন নামক একটি বালিকার হৃদয় উন্মীলনের আখ্যানই মুখ্য। পোস্টমাস্টারকে ঘিরে রতনের আবেগ-চপল, স্নেহকাতর মন কীভাবে চুপিসারে হৃদয়বন্ধনে বাঁধা পড়েছে এবং পোস্টমাস্টার সেই বন্ধনকে উপেক্ষা করে বন্ধনহীনতায় একাকী রতনকে ফেলে তার পূর্বজীবন স্রোতে গা-ভাসিয়ে দিয়েছে সেই বেদনাহত চিত্রই গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশা-প্রাপ্তির এক অনিশ্চয়তার আশাহত কাহিনিপটে নির্মাণ করেছেন। রতন এখানে বন্ধনের বার্তাবাহী। সে প্রকৃতির কন্যারূপে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। সেই যোগসূত্রে নগর জীবন থেকে জীবিকার সূত্রে আগত পোস্টমাস্টারকেও প্রাণের বন্ধনে, প্রীতির বন্ধনে কখন যে বেঁধে ফেলেছে; তা সে টেরও পায়নি। আসলে, এই ‘বন্ধন’ ‘মুক্তি’-রই পরিণাম। রতন মুক্ত পল্লীপ্রকৃতিরই মতো উদার হৃদয়ের অধিকারিণী বলেই, সে অনায়াসেই, স্বল্প সময়ের মধ্যে পোস্টমাস্টারকে আপন করে নিতে পেরেছে। উদার আকাশের মতো মুক্তমনা। তাই, তার বিশুদ্ধ ভালোবাসা দিয়ে অতি সহজেই পোস্টমাস্টার-সহ তার পরিবারের সকল সদস্যকে পর্যন্ত একান্ত আপনার করে নিতে পেরেছে।
আর অপর দিকে, ঐ পোস্টমাস্টার কর্মসূত্রে জীবিকার তাদিদে নগর জীবন থেকে গ্রামের পরিবেশে পাড়ি জমাতে হয়েছে। যে, অচেনা পরিবেশে পড়ে পোস্টমাস্টারের অবস্থা গল্পশিল্পীর ভাষায় —
‘জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে।’২
শহুরে জীবনে পোস্টমাস্টার তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-দিদির স্নেহবন্ধন ছেড়ে ঐ গ্রামজীবনে নির্বাসন তাই জলের মাছকে ডাঙায় তোলার সমান। অথচ, বালিকা রতন পিতৃ-মাতৃহীন, স্নেহবন্ধন বঞ্চিতা চিরবুভুক্ষু সে। পরের বাড়ির কাজকর্মের বিনিময়ে তার জঠরের অন্নসংস্থান ঘটে থাকে। রতন তাই পোস্টমাস্টারের ফাইফরমাশ খাটে; রান্নার বিনিময়ে দুটো খেতে পায়। আর ঐ পোস্টমাস্টারও তার প্রবাসজীবনে আত্মীয়-পরিবার, পরিজনের বন্ধনচ্যুত হয়ে নিঃসঙ্গতায় — সময় কাটানোর জন্য একজন সঙ্গী খুঁজে ফিরছিল। একাকীত্ব কাটাতে সে শখের কবিতা লেখে। হৃদয় দিয়ে যদি কবিতার ভাবরাজ্য তৈরি করার অনুভূতিপ্রবণ মন থাকত; তাহলে সে যে কোনো মানুষের হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারত। নগর জীবনের যাপন চর্যায় অভ্যস্ত পোস্টমাস্টার, গ্রামজীবনকে প্রীতির বন্ধনে, কোনো ভালোলাগা-ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধে নিয়ে আপন করতে পারেনি। তাই গ্রামের কুঠিবাড়ি নগরজীবনে অভ্যস্ত পোস্টমাস্টারের কাছে বিভীষিকাময় হয়ে ওঠে। তাই, নিঃসঙ্গ গ্রামজীবনে ছিটকে-পড়া পোস্টমাস্টার তার আপন পরিবেশ ফিরে পাওয়ার কামনায় মনে মনে কল্পনার ডানা মেলে দেয়। গ্রাম্য পরিবেশে নিজেকে ভালোবাসার-ভালোলাগার আত্মীয়বন্ধনে বাঁধতে না পেরে বরং মুক্তির কামনায় মনে মনে কল্পনা করে —
‘……যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া একরাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকারাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্র সন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।’৩
অর্থাৎ, পোস্টমাস্টার নাগরিক জীবন যাত্রায় চিরভ্যস্ত। যে জীবনের বন্ধনকে সে ছিন্ন করতে পারেনি। বরং সেই বন্ধনেই নিজেকে বন্দী রাখাই তার অভিপ্রায়। কেবল, জীবিকার তাগিদেই বিভুঁইয়ে পাড়ি জমাতে হলেও; তার মন-প্রাণ বাঁধা রয়েছে নগর জীবনেই। তাই, তার এই হাঁফ-ধরা গণ্ডগ্রাম-জীবনের নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ পরিবেশে রতনকে সময় কাটানোর জন্য কাছে চেয়েছে। তাই, পোস্টমাস্টার রতনকে তামাক সেজে দেওয়ার ফরমাস করে। ঐ বালিকার সাথে গল্প করে গা-ছমছমে গ্রাম্য-আঁধার পরিবেশে নিজের ভয়ের ভাব কাটানোর চেষ্টা করে। সুতরাং এদিক থেকে পোস্টমাস্টার আত্মস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যেই রতনের সাহচর্য চেয়েছে। রতনের পারিবারিক জীবনেতিহাসের অনুসন্ধান নেওয়া ঐ রতনকে ভালোবেসে আপন করে নেওয়ার লক্ষ্যে নয় ! কেবল, সময় কাটানোর আছিলা মাত্র। অথচ, রতন তার দুর্বার সারল্যে আর উদার মানসিকতায় পোস্টমাস্টারের মুখ থেকে শোনা, তার বাড়ির খবর যেন রতনেরই অতিপরিচিত প্রিয়জনদেরই খবর। তাই পোস্টমাস্টারের সম্পর্কের মা-দিদি, ভাই-বোনেরা; রতনেরও মা, দিদি, দাদা হয়ে উঠেছে। এই যে আনায়াসে চোখে না দেখেও মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা; তা ঐ উদার প্রকৃতির কন্যা রতনের মতো মুক্তমনা নারীর পক্ষেই সম্ভব। অথচ, পোস্টমাস্টার কোন হৃদয় বন্ধনের সম্পর্কে নয়, নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই রতনকেই আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছে। শুধু তাই নয়; সময় কাটানোর জন্য স্বয়ং পোস্টমাস্টার রতনের লেখাপড়ার দায়িত্ব ও নিয়েছে।
আসলে পোস্টমাস্টার পরিবার প্রিয়জনদের সঙ্গে স্নেহ-প্রেম, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। যে বন্ধন ছেড়ে প্রবাস জীবন তার কাছে ভয়ংকর নিঃসঙ্গ, একাকীত্বে ভরে উঠেছিল। তাই, রতনের সঙ্গে গল্প করে তার সেই নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করত। রতনের সান্নিধ্য, কথার সংলাপের মধ্য দিয়ে পোস্টমাস্টার তার পরিবার প্রিয়জনদের নিবিড় বন্ধন স্মৃতি মনে মনে অনুভব করে। আর ঐ পোস্টমাস্টারের বন্ধন দশা জীবনের বিপরীতে বালিকা রতন সম্পূর্ণ বন্ধনহীনা, মুক্ত প্রকৃতির কন্যা। রতন ও পোস্টমাস্টারের মধ্যে বন্ধনও বন্ধনহীন জীবনের তুলনায়, কবির ‘দুই পাখি’ কবিতার ছবিটি স্মরণে আসে –
‘খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
*******************
এমনি দুই পাখি দোঁহারে ভালোবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে,
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দু-জনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনার।’৪ (‘সোনার তরী’/ ‘দুই পাখি’)
আলোচ্য গল্পেও তেমনই খাঁচার পাখি যে আসলে নাগরিক জীবনচর্যায় অভ্যস্ত পোস্টমাস্টার। যে ঐ দমবন্ধ জীবনের বন্ধনদশা থেকে প্রবাসে ছিটকে পড়ে খাঁচার পাখির মতো হাপিত্যেশে কোনোরকম সময় কাটানোর চেষ্টা করছে। আর বনের পাখি যে ঐ বালিকা রতন; তাতে পাঠকের বোধ করি বুঝতে আর বাকি রইল না।
তাই ঐ অক্ষরহীনা বন্ধনমুক্ত বনের পাখিরূপ বালিকা রতনকে অক্ষর শেখানোর ভার নিল পোস্টমাস্টার। অতি অল্পদিনেই রতন যুক্তাক্ষর শিখে গেল। এই সূত্রেই রতন তার দাদাবাবু তথা পোস্টমাস্টারের হৃদয় সান্নিধ্য লাভ করে। পোস্টমাস্টারকে কখন যে মনের অজান্তে একান্ত আপনার করে ফেলে, তা তার আচরণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ, শহুরে বুদ্ধির পোস্টমাস্টার বালিকা রতনের হৃদয়, পাঠ নিতে ব্যর্থ। পোস্টমাস্টারের মুখে ‘রতন’ ডাকটি শোনার জন্য বালিকা উন্মুখ হয়ে থাকে। ইচ্ছে করে একডাকে হাঁক শোনায় না। দরজার বাইরে রতন অপেক্ষা করে, কখন দাদাবাবুর ডাক পড়বে। দু-চারটে হাঁক-ডাকের পর, তবেই সে দরজার বাইরে থেকে ভিতরে প্রবেশ করত। স্নেহবুভুক্ষু রতন, পোস্টমাস্টারের নিঃসঙ্গ, একাকীত্বের মাঝে সঙ্গ দিয়ে, সেবায়-পরিচর্যায় স্নেহের বন্ধন প্রত্যাশা করেছিল। বয়ঃসন্ধির আলো-আঁধারে বালিকা রতনের স্নেহ সাহচর্য তথা, বন্ধন প্রত্যাশা পোস্টমাস্টারের অনুভবের বাইরে। অথচ, গ্রাম্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এসে পোস্টমাস্টার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে, বালিকা রতন কবিরাজ ডেকে এনে বটিকা সেবন করায়। সারারাত শিয়রে জেগে পোস্টমাস্টারের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। পীড়িত পোস্টমাস্টার রতনের সেবাময়ী হাতের স্পর্শ পেয়ে শাখা-পলা-পরা আপন পত্নীর সেবা-সান্নিধ্য অনুভব করেছে। আত্মীয়-পরিজন থেকে বহুদূরে নির্বাসিত, পীড়িত জীবনে প্রিয়জনদের সান্নিধ্য মনে মনে, কল্পলোকে অনুভব করেছে, অথচ জননীর পদে বসে রতন যে সেবা-শুশ্রূষা করে গেল হৃদয়-প্রাণ-মন দিয়ে সে খবর রাখতে চাইল না পোস্টমাস্টার। পোস্টমাস্টার যে বন্ধনে বন্দী, সেই বন্ধন থেকে পোস্টমাস্টারকে টেনে বের করে নতুন কোন বন্ধনে রতন বাঁধতে পারেনি। রতন, বন্ধনহীনা রয়েই গেল। আর তারই চরম পরিণতি গল্পের চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে দেখা গেল। পোস্টমাস্টার গ্রামের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে বদলি চেয়ে, তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দরখাস্ত লিখে পাঠাল। সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে; চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে পোস্টমাস্টার তার পূর্বস্থানে ফিরে যেতে উদ্যোগী হল। রতনের সেবায় সুস্থ হয়ে ওঠা পোস্টমাস্টার একদিন শেষ সন্ধ্যায় তার ঐ বিদায়ের কথা রতনকে জানিয়ে দিল। সেই জানিয়ে দেওয়াটা যেন নেহাতই কর্তব্যের। শুনে রতন ভয়ংকর অসহায়বোধ করল। এতদিন সে পোস্টমাস্টারের স্নেহসান্নিধ্যের আশ্রয়ে একটা ছায়ালাভ করেছিল। সেই ছায়া সরে যাওয়ার আশঙ্কায় সে তার পোস্টমাস্টার তথা, দাদাবাবুকে সকাতরে সুধায় — ‘দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?’৫
উত্তরে পোস্টমাস্টার উদাসীনভাবে সুধায় — ‘সে কী করে হবে।’
এভাবে রতনের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন শেষপর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়। রতনের নারীহৃদয়ের গভীর তলদেশে ডুব দিয়ে তার মনের ভাষা অনুধাবন করার মতো ক্ষমতা নেই পোস্টমাস্টারের। পূর্বেই বলেছি, পোস্টমাস্টারের দার্শনিক কবিসুলভ মন নেই। তাই সে বালিকা রতনের হৃদয় বন্ধনে সাড়া দিতে পারেনি। সেই বন্ধন প্রত্যাশী নারীর হৃদয়গতি টেরও পায়নি। ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পের নিরঞ্জনেরা যামিনীদের কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনি। কারণ, নিরঞ্জন শহুরে পরিবেশে গিয়ে প্লেগ রোগে মারা গিয়েছিল। সেই সংবাদ না পেয়ে অজ্ঞাত যামনীরা ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন গুনে যায় পুরুষের বন্ধন প্রত্যাশায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘ছিপ’-এর ইঙ্গিতে যামিনীর মতো নারীদের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ যন্ত্রণাকে রোম্যান্টিকতার ঢঙে গল্পশিল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বালিকা রতনের বন্ধন প্রত্যাশা ও সেই প্রত্যাশার প্রত্যাখ্যানের নির্মম পরিণতিসূত্রে পোস্টমাস্টারের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন জীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতির এক তত্ত্বদর্শন। রতন যখন বন্ধন প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে; বৈষয়িক বুদ্ধির অধিকারী পোস্টমাস্টার রতনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন —
‘রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন, তাঁকে বলে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।’৬
কিন্তু, রতনের নারীহৃদয় কেবল যত্নআত্তি চায় না। চায় না কেবল দু-বেলা ভরপেট খেয়ে-পরে বাঁচতে। কারণ, মানুষ শুধু দেহে বাঁচে না; মনেও বাঁচে। সেই বাঁচার মর্মার্থ বৈষয়িক পোস্টমাস্টারের বোঝার ক্ষমতা নেই। নিম্নবৃত্তীয়, অনাথিনী, অশিক্ষিতা বালিকার সাথে স্নেহ-সম্পর্কের বন্ধন-ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্কের বন্ধনে বাঁধবার কল্পনাও করতে পারেনি পোস্টমাস্টার। পোস্টমাস্টার একটি সংসারসীমার পারে বন্দী। সেই বন্ধন মাঝে, সমাজ সংসারকে উপেক্ষা করে রতনকে জীবন সাহচর্য দেওয়ার কথা ভাবতেও পারেনি। কেবল রতনের আর্থিক সংকটের কথা ভেবে পোস্টমাস্টার বিদায়কালে শুধুমাত্র পথখরচটুকু রেখে, বেতনের সমস্ত অর্থ তাকে দিতে চেয়েছে। কিন্তু, রতন যা চেয়েছে তা না পাওয়ায়, ব্যথিত চিত্তে সেই অর্থ গ্রহণ করতে চায়নি। পোস্টমাস্টার যেমন রতনের হৃদয়বন্ধন প্রত্যাখ্যান করেছে, তেমনই রতনও পোস্টমাস্টারের দেওয়া অর্থ প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে নারীর আত্মমর্যাদা, তার ব্যক্তিত্ববোধকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে।
রতন তার দাদাবাবুকে হৃদয়বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারেনি তাই পোস্টমাস্টার রতনকে ফেলে অনায়াসে নৌকায় চড়ে বসল বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রার লক্ষ্যে। তার মন-প্রাণ সেখানে বাঁধা রয়েছে। অথচ পোস্টমাস্টারের মনে কোথাও একটু স্নেহপুত্তলি লুকিয়ে ছিল। আর সেই স্নেহের লুক্কায়িত কোমল স্পর্শটুকু উঁকি দিয়ে ওঠে যখন পোস্টমাস্টার নদীবক্ষে পালতোলা নৌকায় বসে নদীতীরবর্তী শ্মশান সম্মুখে উপস্থিত হন। সেই শূন্য শ্মশান পরিবেশে উপস্থিত হয়ে পোস্টমাস্টারের মনে হল, তিনি আবার ফিরে যান ঐ অনাথিনী বালিকাকে সঙ্গে করে আনবার জন্য। কিন্তু নির্জন শ্মশান পরিবেশে উপস্থিত হয়ে পোস্টমাস্টার নিজের দোলাচল মনকে সান্ত্বনা দিতে দার্শনিকসুলভ ভঙ্গিতে বলেছে —
জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।’৭
আর এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়ে, পোস্টমাস্টার এগিয়ে চলে আপন জীবন প্রবাহে। রতনের মতো অনাথিনী বালিকার প্রতি সমবেদনা থাকতে পারে। কিন্তু কোনো বন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলা যায় না। তাই অনায়াসে ঐ বালিকার বন্ধন প্রত্যাশাকে প্রত্যাখ্যান করে, আপন সুখী গৃহবন্ধনের উদ্দেশ্যে ফিরে চলেছেন। অথচ, ওদিকে রতন এক আকাশ স্বপ্ন নিয়ে পোস্টমাস্টারের ফিরে যাওয়ার পথ চেয়ে বসে রয়েছে। সে কেবল নির্জন পোস্টঅফিসের চারপাশে ঘুরে চলেছে। রতনের স্থির বিশ্বাস — ‘যদি দাদাবাবু ফিরিয়া আসে।’ — এই ক্ষীণ প্রত্যাশাটুকু নিয়ে অনাথিনী বালিকা রতন পোস্টমাস্টারের পথপানে চেয়ে রয়েছে। গল্পশেষে লেখকের দার্শনিক জ্ঞানানুভূতির মধ্য দিয়ে ‘বন্ধন’ ও ‘বন্ধনমুক্তি’-র প্রত্যাশায় জীবন সম্পর্কে দিয়েছে এক মহাকাব্যিক উপলব্ধি। জগতের বন্ধন যেমন সত্য; তেমনই মুক্তিও সত্য। জীবন সম্পর্কে এমন বন্ধনও বন্ধনমুক্তির তত্ত্বকথা কবির কাব্যানুভূতিতেও ধরা পড়েছে —
‘……এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন — ‘যেতে নাহি দিব হায়।’ হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।...’৮ (‘সোনার তরী’ / “যেতে নাহি দিব”)
এভাবে, দুই নর-নারীর হৃদয়ের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির তথা, অনন্ত বিচ্ছেদরূপ বিরহের যে বাতাবরণ গল্পশেষে উঠে এসেছে, তাতে লেখকের জীবন সম্পর্কে ঐ তত্ত্বানুভূতিতে জগৎ ও জীবনের মাঝখানে গল্পপাঠককে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। গল্পশেষে এই বিশেষ তত্ত্বকথার উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-গল্পমানসের সেই ‘বন্ধন’ ও ‘বন্ধনমুক্তি’-র প্রত্যাশা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে, রবীন্দ্র প্রতিভা অমৃত নির্ঝর। তাই গল্পকথার ভিতর দিয়ে জীবনের নানা তত্ত্বকথাকে দার্শনিক সুলভ ভঙ্গিতে স্বভাবগীতি কবির সুরে উচ্চারণ করতে পারেন। মানবিক মূল্যবোধকে নিয়ে গল্পভাষায় করেন বিচার বিশ্লেষণ। হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে, জীবনের তত্ত্বকথা রূপায়নের ভিতর দিয়ে কবিসুলভ দৃষ্টিতে প্রেমধর্মের জয় ঘোষণা করেন। আলোচ্য গল্প কাহিনির ভিতর দিয়ে সেই হৃদয়ধর্মের তত্ত্বকথায় — ‘বন্ধন’ ও ‘বন্ধনমুক্তি’-র প্রত্যাশা রূপায়িত হয়েছে। গল্পশেষে এমন ঐ তত্ত্বকথা রূপায়ন প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক তাই বলেছেন—
‘কলাকৌশলের দিক হইতে এই তত্ত্বের উদয় না হইলেই ভাল হইত; তবু যাহাই হউক, এমনই করিয়া পোস্টমাস্টার ও রতনের দুঃখ একটা উদাস-সকরুণ পরিসমাপ্তি লাভ করিল এবং সেই অব্যক্ত মর্মব্যথা যেন সমস্ত বিশ্বে পরিব্যপ্ত হইয়া একটি অপূর্ব সুরের জগৎ সৃষ্টি করিল।’৯
সেই সুর হল ‘বন্ধন’ ও ‘বন্ধনমুক্তি’-র দুরন্ত প্রত্যাশার সুর। এই গল্পের সঙ্গে ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশার প্রতিতুলনা চলে। পোস্টমাস্টার ও ফটিক উভয়েই বিপরীত পরিবেশে আত্মীয়বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দুর্বিষহ নির্বাসন জীবন ভোগ করেছে। ‘ছুটি’-র ফটিক বন্ধনমুক্তির প্রত্যাশায় পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন থেকে চিরমুক্তির প্রার্থনা করেছে। কিন্তু, পোস্টমাস্টার, বালিকা রতনের সঙ্গে গড়ে ওঠা আত্মীয় সম্পর্কের বন্ধন প্রত্যাখ্যান করে; তথা সেই বন্ধন ছিন্ন করে স্ব-স্থানে ফিরে গেছে। পোস্টমাস্টারের ঐ ফটিকের মতো ছুটি মেলেনি।বরং চাকরি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে পূর্ব সংসার জীবনের বন্ধনে আটকে যেতে হয়েছে। এভাবে অসংখ্য রবীন্দ্র ছোটোগল্পে ‘বন্ধন’ ও ‘বন্ধনমুক্তি’-র প্রত্যাশা বিষয়টি প্রায়ই ঘুরে-ফিরে এসেছে।
তথ্যসূত্র
১. রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ - জৈষ্ঠ্য ১৩৫১, পৃষ্ঠা ১৪২।
২. রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চদশ খণ্ড), শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা, ফাল্গুন ১৩৭০, ১৮৮৫ শক। পৃষ্ঠা ৪১২।
৩. তদেব, ঐ।
৪. রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা, চতুর্থ সংস্করণ - জৈষ্ঠ্য ১৩৫১, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৫।
৫. রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চদশ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৫।
৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী (পঞ্চদশ খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১৬।
৭. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১৭।
৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩।
৯. রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা - নীহাররঞ্জন রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, প্রকাশক, অমিতাভ সেন, ষষ্ঠ মুদ্রণ - ২৫ বৈশাখ, ১৪১৬। পৃষ্ঠা ৩৫০।