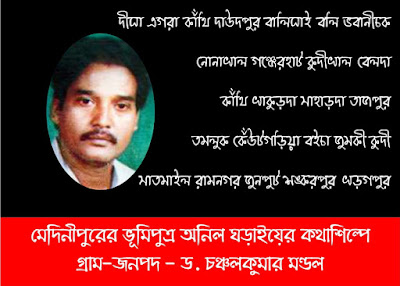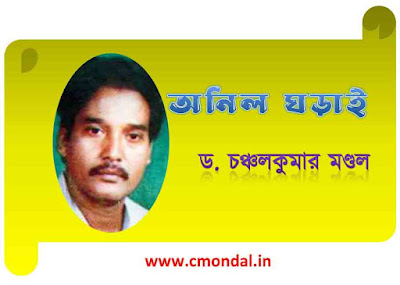জাত-পাতের ব্যাকরণ ও রবীন্দ্র-নাটক —ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল
 |
জাত-পাতের ব্যাকরণ ও রবীন্দ্র-নাটক
—ড. চঞ্চলকুমার মণ্ডল
SACT – 1, বাংলা বিভাগ, সবং সজনীকান্ত
মহাবিদ্যালয়
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বের বিস্ময়। মহাকাব্য রচনা না করেও তিনি মহাকবি।
আবার, একাধারে নট ও নাট্যকার। সাহিত্যের বিভিন্ন স্রোতে তাঁর প্রতিভা কেবল
প্রবাহিত মাত্র নয়। সেই সকল সাহিত্য শাখায় নানা বর্ণের-নানা গন্ধের ফুল ফুটিয়ে
বিশ্ববাসীকে তিনি করেছেন আমোদিত। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি-কলার ভেতরে রয়েছে যেমন গূঢ়
তত্ত্বকথা, তেমনি মানব মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বকবি হয়েছেন প্রতিবাদ মুখরও। বাংলা
সাহিত্যের সবচাইতে জোরালো প্রতিবাদী মাধ্যম হল নাট্য শিল্প। এই নাট্য রচনার মধ্য
দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেমন জীবনের গুঢ়তর সত্যকে ছুঁতে চেয়েছেন; তেমনি মানুষে-মানুষে
অস্পৃশ্যতা, জাত-পাতের বদ্ধ প্রাচীরকে দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে গুড়িয়ে দিয়ে চেয়েছেন।
জাতের নামে বজ্জাতির এই প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য কবিতায়ও বার-বার ঘোষণা
করেছেন। ‘গীতাঞ্জলী’র ‘ভারত তীর্থ’ থেকে ‘সোনার তরী’র ‘বসুন্ধরা’ কবিতায় তিনি
জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মানবতার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। আবার, ‘পুনশ্চ’
কাব্যের ‘শুচি’, ‘মুক্তি’, ‘মানবপুত্র’, ‘শিশুতীর্থ’, ‘প্রেমের সোনা’, ‘স্নান
সমাপন’ কবিতা থেকে শুরু করে ‘নৈবেদ্যে’র কবিতাগুচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ঘুচিয়ে
মানবতারই আহ্বান করেছেন। কেবল কাব্য ক্ষেত্রেই নয়; কথাসাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ
হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র রচনা করেছেন। মুসলিম মাত্রেই ‘ম্লেচ্ছ’, ‘যবন’
আর হিন্দু অর্থে ‘জাতিশ্রেষ্ঠ’ এই ধারণার পরিবর্তন প্রথম আনতে চেয়েছিলেন স্বয়ং
রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ‘বৌ-ঠাকুরানীর হাট’ কিম্বা ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস, এমনকি, ‘মুকুট’,
‘দুরাশা’, ‘সমস্যা পূরণ’, ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ এমনকি জাতপাতের সংস্কারের বিরুদ্ধে
বিদ্রূপ হেনেছেন। আবার ‘মানুষের ধর্ম’,
‘হিন্দু-মুসলমান’, ‘শিক্ষা’ প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের
সমস্যাকে তুলে ধরে জাত-পাতের সংকটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন।